জাতিসংঘের প্রস্তাবিত শিক্ষা বাজেট থেকে আমরা কত দূরে?
প্রকাশিত:
১৫ মে ২০২৫ ১০:৪৯
আপডেট:
১০ জানুয়ারী ২০২৬ ১০:২১
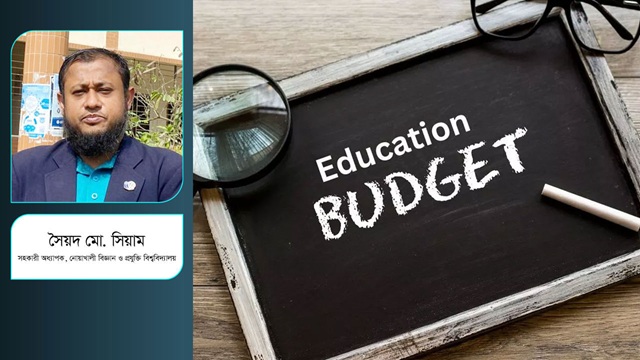
শিক্ষা বাজেট হচ্ছে জাতীয় বাজেটের শিক্ষাখাতে সরকারের বার্ষিক বরাদ্দ যা দেশের উন্নত মানবসম্পদ ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী তৈরির পাশাপাশি সামাজিক সাম্যতা এবং টেকসই উন্নয়নের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। প্রতিবছরই জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে উল্লেখযোগ্য বরাদ্দের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার শিক্ষার মান উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নে কাজ করে যাচ্ছে।
২০২৩-২৪ অর্থবছরে সরকার শিক্ষাখাতে ৮৮ হাজার ১৬২ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছিল। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ সাত দশমিক ৪২ শতাংশ বাড়িয়ে ৯৪ হাজার ৭১০ কোটি টাকা করে যা মোট বাজেটের প্রায় ১২ শতাংশ। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতির ভিত তৈরিতে ভূমিকা রাখছে।
শিক্ষাক্ষেত্রের এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হলে সরকারকে অবশ্যই ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়, শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ মোট বাজেটের ১০-১২ শতাংশর মধ্যেই থাকে এবং যা মোট দেশজ উৎপাদনের ২ শতাংশের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে।
বিভিন্ন গবেষণা ও উন্নয়নমূলক প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে মাথাপিছু বার্ষিক বিনিয়োগের পরিমাণ বাংলাদেশে ৫ ডলার, শ্রীলঙ্কায় ১০ ডলার, ভারতে ১৪ ডলার, মালয়েশিয়াতে ১৫০ ডলার ও দক্ষিণ কোরিয়ায় ১৬০ ডলার। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে শিক্ষা বাজেট জিডিপির ৬ শতাংশ এবং মোট জাতীয় বাজেটের ২০ শতাংশ হওয়ার কথা। কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যয় ২.৩ কিংবা ২.৪ শতাংশ এবং মোট বাজেটের ১৫ শতাংশের নিচে অবস্থান করছে, যা আফ্রিকার অনেক দেশ থেকেও কম।
তবে প্রশ্ন হচ্ছে, শুধু শিক্ষা বাজেট বাড়ালেই কি শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত মানে আমরা পৌঁছে যাব? শিক্ষা বাজেট বাড়ানোর সঙ্গে এর সঠিক ও উপযুক্ত ব্যবহার প্রয়োজন। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় বরাদ্দের একটি অংশ দুর্নীতি খেয়ে ফেলে, তাহলে সমস্যা কোথায়? সমস্যা হলো বাংলাদেশে শিক্ষা খাত নিয়ে কাজ করার জন্য পর্যাপ্ত দক্ষ ও যোগ্য লোক গড়ে তোলা যায়নি।
শিক্ষার মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সঠিক পরিকল্পনা আমাদের নেই, আমরা এখনো গতানুগতিক ধারায় এমএ-বিএ পাস করানোর পরিকল্পনায় আছি। দেশের জন্য প্রয়োজনীয় জনশক্তি তৈরির শিক্ষা পরিকল্পনা আমাদের নেই। সঠিক পরিকল্পনা, সঠিক বাস্তবায়ন এবং যোগ্য লোক দরকার শিক্ষার উন্নতির জন্য। তাহলেই বাজেট বাড়িয়ে কাজ হবে অন্যথায় বাজেট বাড়ালেও তা যথাযথ খরচ হবে না, আর যা খরচ হবে তার একটি অংশ দুর্নীতিবাজদের পকেটে যাবে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের প্রাক্তন পরিচালক অধ্যাপক ছিদ্দিকুর রহমানের প্রবন্ধে উঠে আসে শিক্ষা সংক্রান্ত খাতে এমনিতেই বরাদ্দ কম, তার ওপর পরিকল্পনাহীন বরাদ্দ আমাদের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে বোঝায় পরিণত করছে। এক সময় হয়তো আমাদের কৃষি উৎপাদন, শিল্প উৎপাদনসহ আরও অনেক সেবা খাতে লোক পাওয়া যাবে না। যা আমাদের জন্য ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে।
শিক্ষা খাতে রাষ্ট্রের বিনিয়োগ বাড়াতে হবে, যাতে দেশ উন্নতমানের ও কাঙ্ক্ষিত রিটার্ন যেন আমরা পায়। আগামীর বাংলাদেশের উন্নয়নে সর্বাগ্রে গুরুত্ব দিতে হবে শিক্ষাখাতকে কেননা কেবলমাত্র এই খাতের বরাদ্দ তথা বিনিয়োগ সঠিক ব্যবস্থাপনা আর মনিটরিং আওতায় এনে ব্যয় করলে দেশের জন্য সর্বোচ্চ পরিমাণ রেট অব রিটার্ন নিয়ে আসতে পারে।
শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা, মাদ্রাসা ও ধর্মীয় শিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, চিকিৎসা শিক্ষা, প্রকৌশল শিক্ষা কৃষি শিক্ষাসহ যাবতীয় পেশাগত শিক্ষা, শিক্ষকদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা নিয়ে গবেষণাসহ প্রতিটি ক্ষেত্রের কথা আলাদাভাবে চিন্তা করে বাজেট প্রণয়ন করে বরাদ্দ দিতে হবে।
সরকারকে এজন্য কৌশলী হতে অগ্রাধিকার চাহিদাগুলোর কথা চিন্তাও এগিয়ে যেতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মানসম্মত ও আদর্শ শিক্ষা নিশ্চিতকরণে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত একটি যুক্তিযুক্ত সীমার মধ্যে রাখা প্রয়োজন, যা প্রাথমিক স্তরের জন্য ১:৩০, নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের জন্য ১:৪০ এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ১:২৫—এর বেশি নয় একই সাথে শিক্ষায় একীভূত হওয়া নিশ্চিতকরণে শিক্ষার্থীবান্ধব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার বিষয়টিও গুরুত্ব বহন করে, অথচ এসব বিষয় নিশ্চিতকরণের কোনো প্রতিফলন বাজেটে ঘটেনি।
ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের মতে, শিক্ষার মান বিচারে দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে পিছিয়ে বাংলাদেশ। ১৩০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৭৭তম। ভারত ২৭তম, শ্রীলঙ্কা ৩৮তম, পাকিস্তান ৬৬তম ও নেপাল ৭০তম। বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) থেকে প্রাপ্ত কিছু তথ্য, যেমন মাধ্যমিক পর্যায়ে ৩০ শতাংশ শিক্ষকের কোনো ধরনের প্রশিক্ষণ নেই এবং দেশের ৩০ শতাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কোনো বিজ্ঞানাগার নেই। এই দুটি বিষয়ই কিন্তু শিক্ষার মানের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত অন্যতম নিয়ামক।
প্রথম বিষয়টি নিয়ে অনেক কথা হয়, অর্থাৎ শিক্ষকদের মান বৃদ্ধি করার কথা বলা হয়, অর্থও খরচ করা হয়, কিন্তু এর কতটা কাজে লাগানো হয়, সেটি নিয়ে কোনো ধরনের ‘ফলোআপ’ কার্যক্রম নেই। একইভাবে বিজ্ঞান শিক্ষায় আমাদের শিক্ষার্থীরা, বিশেষ করে গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ভীষণভাবে পিছিয়ে আছে।
তাদের কীভাবে বিজ্ঞান শিক্ষায় আগ্রহী করে তোলা যায় তার সঠিক উল্লেখ থাকা প্রয়োজন শিক্ষা বাজেটে। একাধিক জরিপ প্রতিবেদনে দেখা যায়, অষ্টম শ্রেণির অর্ধেকের বেশি শিক্ষার্থীর বাংলা, ইংরেজি ও গণিতে কাঙ্ক্ষিত মানের দক্ষতা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হয়, তখন এই দুর্বলতা চোখে পড়ে। পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলে এগুলো প্রকাশিত হয় না।
প্রতি অর্থবছরে শিক্ষা এবং প্রযুক্তি মিলিয়ে বাজেট দেওয়া হয়। শিক্ষার বাজেটটা যদি আমরা আলাদা করে দেখি, তাহলে এটা বাজেটের শতকরা ১২ ভাগের বেশি হয় না। যা জিডিপির ২ শতাংশের মতো।
বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যেও সবচেয়ে কম বাজেট থাকে শিক্ষাখাতে সেটি হচ্ছে বাংলাদেশ। এই বরাদ্দের মধ্যেও অনেক ফাঁকি আছে, নানামুখী শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে সেটা ভাগ হচ্ছে নানাভাবে কেন্দ্রীয়ভাবে শিক্ষার উন্নয়নে এককভাবে তা ব্যবহার করা যায় না।
তবে বাজেটে শিক্ষাখাতে যেটুকু বরাদ্দ হয়, তার অধিকাংশই ব্যয় হয় শিক্ষক, কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের বেতন ভাতা ও প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো নির্মাণে। কিন্তু শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য যেসব কার্যক্রম থাকে সেখানে বরাদ্দ পরিমাণ অনেক কম, দেখা যায় গবেষণা বা প্রশিক্ষণের জন্য বাজেট বরাদ্দ থাকে একেবারে নামমাত্র।
শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণা ও আর স্কুল-কলেজ পর্যায়ে শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ দরকার। না হলে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থায় তার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এই দুই খাতেই বরাদ্দ নেই। শিক্ষা একটি সার্বিক বিষয়—এরজন্য গবেষণা, যোগ্য শিক্ষক এবং অবকাঠামো দরকার হয়। বাজেটে তার কোনো পরিকল্পনার ছাপ নেই বললেই চলে ফলশ্রুতিতে দেখা যায় আমরা অন্যদের তুলনায় পিছিয়ে পড়ছি প্রতিনিয়তই।
আবার অন্যদিকে দেখা যায় সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি দেশের অনেক বেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই বেসরকারি। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা এই তিন স্তরে বিন্যস্ত সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা। তাছাড়া মাদরাসা, ইংলিশ মিডিয়াম, ইংলিশ ভার্সনসহ নানা ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিদ্যমান রয়েছে।
এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রায় ১৫ থেকে ২০ লাখ শিক্ষক-কর্মচারী চাকরি করছেন এবং ৫ কোটিরও বেশি শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছেন। শিক্ষার সাথে মূলত সম্পৃক্ত আছেন দেশের সব মানুষ। একইসঙ্গে সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রাম-শহর, ছেলেমেয়ে, তৃতীয় লিঙ্গ শিক্ষার্থী, সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা—সব ক্ষেত্রে বৈষম্য কমাতে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।
তাই মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ আর শিক্ষার উন্নয়নের চলমান ধারা অব্যাহত রাখতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ইউনেস্কো—আইএলও ঘোষিত জাতীয় বাজেটের ২০ শতাংশ করা এবং সেই সাথে খাতওয়ারী বাজেটের সুষম বণ্টন প্রক্রিয়া ও ব্যয় নির্ধারণে যথাযথ পরিকল্পনা আর সুস্পষ্ট জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি।
সৈয়দ মো. সিয়াম ।। সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষা বিভাগ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
সম্পর্কিত বিষয়:
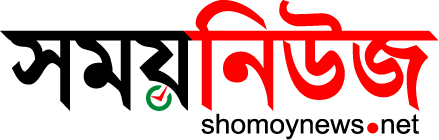



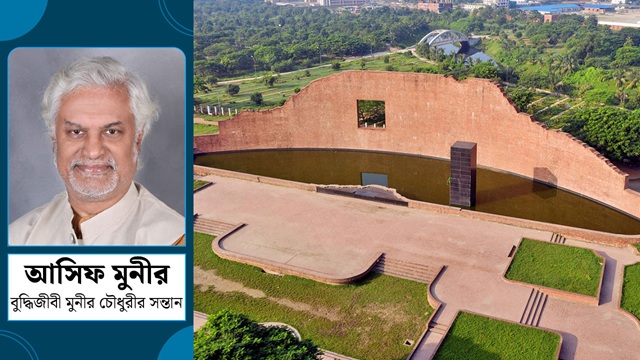

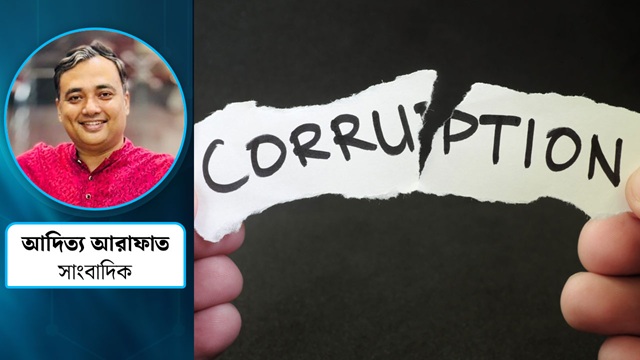




আপনার মূল্যবান মতামত দিন: