বাড়ছে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্সের ভয়াবহতা, সমাধান কি আছে?
প্রকাশিত:
২৪ নভেম্বর ২০২৫ ১৩:৫২
আপডেট:
৯ জানুয়ারী ২০২৬ ০২:৩৪

অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (AMR) বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে বড় জনস্বাস্থ্য হুমকিগুলোর মধ্যে অন্যতম। যখন জীবাণু (যেমন ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক ও পরজীবী) নিজেদের পরিবর্তন করে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালস (অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টিভাইরাস, অ্যান্টিফাঙ্গাল এবং অ্যান্টিপ্যারাসাইটিক) ওষুধকে অকার্যকর করে তোলে, তখন সেই অবস্থাকে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স বলা হয়। এর ফলে সাধারণ সংক্রমণও কখনো কখনো মারাত্মক বা নিরাময়-অসাধ্য হয়ে ওঠে। ফলে বেড়ে যায় মৃত্যুঝুঁকি।
প্রতিবছর সারাবিশ্বে World Antimicrobial Resistance Awareness Week (WAAK) ‘বিশ্ব অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রতিরোধ সচেতনতা সপ্তাহ (১৮-২৪ নভেম্বর) পালন করা হয়। ২০২৫ সালে দিবসটির প্রতিপাদ্য হলো ‘এখনই পদক্ষেপ নিন: আমাদের বর্তমানকে রক্ষা করুন, আমাদের ভবিষ্যতকে সুরক্ষিত করুন’।
এই প্রতিপাদ্যটি অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রতিরোধের ক্রমবর্ধমান হুমকি মোকাবিলায় জরুরি এবং সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়।
বিশ্বব্যাপী অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স-এর কারণে মৃত্যুর হার বাড়ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর মতে, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্সের ফলে ২০১৯ সালে সরাসরি ১.২৭ মিলিয়ন মৃত্যুর কারণ হয়েছিল এবং ৪.৯৫ মিলিয়ন মৃত্যুর জন্য অবদান রেখেছিল।
পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০৫০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা প্রতি বছর ১০ মিলিয়ন বা তারও বেশি হতে পারে। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্সের মৌলিক কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো জীবাণুর প্রাকৃতিক বিবর্তন প্রক্রিয়া। কিন্তু মানুষের ভুল ও অযাচিত ব্যবহার এই প্রক্রিয়াকে আরও দ্রুত ও সহজ করে দিচ্ছে।
কখনো কখনো জীবাণু বা ব্যাকটেরিয়ার জেনেটিক উপাদানে আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে, যার ফলে তারা ওষুধের টার্গেট বা বাইন্ডিং সাইট পরিবর্তন করতে পারে। এছাড়াও ব্যাকটেরিয়া এমন কিছু অ্যানজাইম তৈরি করে যা অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধটিকে ধ্বংস বা নিষ্ক্রিয় করে দেয়।
ব্যাকটেরিয়া তার প্রবেশদ্বার পরিবর্তন করে বা পাম্প তৈরি করে যা ওষুধকে কোষের ভেতর প্রবেশ করতে দেয় না অথবা প্রবেশ করলেও আবার দ্রুত বের করে দেয়। আবার একটি রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া সহজেই তার রেজিস্ট্যান্স জিন অন্য ব্যাকটেরিয়ার সঙ্গে বিনিময় করতে পারে, যা রেজিস্ট্যান্সকে দ্রুত ছড়িয়ে দেয়।
রেজিস্টান্স তৈরি হওয়ার মানুষ্য সৃষ্টি প্রধান কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালসের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার যেমন ভাইরাল সংক্রমণ (সাধারণ সর্দি, ফ্লু) বা অন্যান্য সংক্রমণ যেখানে অ্যান্টিবায়োটিক দরকার নেই সেখানেও ব্যবহার করা, রোগী সুস্থ বোধ করার পর ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই অ্যান্টিবায়োটিক কোর্স বন্ধ করে দেওয়া।
এর ফলে দুর্বল ব্যাকটেরিয়াগুলো মরে যায়, কিন্তু শক্তিশালী ও রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়াগুলো বেঁচে থাকে। এর পাশাপাশি দ্রুত বৃদ্ধির জন্য বা সংক্রমণ প্রতিরোধে কৃষি, মাছ ও পশুপাখি পালনে অনেকদিন ধরেই অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ব্যবহার করা হচ্ছে।
তাছাড়া মানুষের হাসপাতাল বা সামাজিক চলাচলে দুর্বল স্যানিটেশন ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যবিধির কারণে রেজিস্ট্যান্ট জীবাণু দ্রুত ছড়ায়।
বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিশ্বের প্রায় সব দেশেই অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সের সমস্যা রয়েছে। বিশেষত ভারত, চীন, বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং নাইজেরিয়ার মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলো এই ঝুঁকিতে সবচেয়ে বেশি।
ভারতে নিওনেটাল সেপসিস (নবজাতকের রক্তে সংক্রমণ) চিকিৎসায় ব্যবহৃত একাধিক ফার্স্ট-লাইন অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে উচ্চমাত্রার রেজিস্ট্যান্স দেখা যায়।
গ্রিস ও ইতালিতে নির্দিষ্ট কিছু গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার (Klebsiella Pneumoniae) ক্ষেত্রে উচ্চমাত্রার কার্বাপেনেম রেজিস্ট্যান্স একটি গুরুতর উদ্বেগের কারণ।
বর্তমানে এই দেশগুলো অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল স্টুয়ার্ডশিপ প্রোগ্রাম তৈরি, নজরদারি শক্তিশালীকরণ এবং অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার সীমিত করার জন্য কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে।
বাংলাদেশে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্সের-এর পরিস্থিতি হলো রেজিস্ট্যান্সের হার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে নির্দিষ্টভাবে ‘কতগুলো ওষুধের অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স হয়েছে’ এই সংখ্যাটি সুনির্দিষ্ট নয়, কারণ এটি এলাকা এবং হাসপাতাল ভেদে প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়।
তবে বিভিন্ন জাতীয় গবেষণায় দেখা গিয়েছে, তৃতীয় প্রজন্মের সেফালোস্পোরিন (Third-generation Cephalosporins) E. coli এবং Klebsiella Pneumoniae-এর মতো সাধারণ ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে এই অ্যান্টিবায়োটিকগুলোর কার্যকারিতা বহুল পরিমাণে কমে গেছে।
কার্বাপেনেম (Carbapenems) ‘লাস্ট-রিসোর্ট’ অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবে বিবেচিত হলেও, বাংলাদেশে এর বিরুদ্ধে কার্বাপেনেম-রেজিস্ট্যান্ট অ্যান্টারোব্যাকটেরিয়াসি-এর সংক্রমণ বাড়ছে, যা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক।
ফ্লুরোকুইনোলোন (Fluoroquinolones) যা টাইফয়েড জ্বরের চিকিৎসায় রেজিস্ট্যান্সের হার অনেক জায়গায় ৭০ শতাংশ ছাড়িয়েছে। এছাড়া আরও কিছু ওষুধের বিরুদ্ধে জীবাণুর রেজিস্ট্যান্স হার সত্যিই আতঙ্কিত হওয়ার মতো।
অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স কেবল মানুষের সমস্যা নয়; এটি প্রাণী এবং পরিবেশের মধ্যেও আবর্তিত। এই সমস্যা মোকাবিলায় ওয়ান হেলথ (One Health) ধারণাটি অপরিহার্য।
ওয়ান হেলথ হলো এমন একটি সমন্বিত প্রচেষ্টা যা মানুষের স্বাস্থ্য, অন্যান্য প্রাণীর স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের স্বাস্থ্যকে এক ছাতার নিচে এনে কাজ করে।
চিকিৎসকদের জন্য অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল স্টুয়ার্ডশিপ গাইডলাইন প্রণয়ন ও কার্যকর করা, মাছ-পশুপালনে অপ্রয়োজনীয় অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার বন্ধ করা, রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকা দেওয়া এবং উন্নত খামার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। সেই সাথে ওষুধ তৈরির বর্জ্য এবং পয়ঃনিষ্কাশনের মাধ্যমে রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া যাতে জল ও মাটিতে না ছড়াতে পারে তা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
চিকিৎসক, পশুচিকিৎসক, কৃষি বিশেষজ্ঞ, পরিবেশবিদ এবং মাইক্রোবায়োলজিস্টদের সমন্বিত ডেটা আদান-প্রদান ও কৌশল প্রণয়নের মাধ্যমে রেজিস্ট্যান্সের উৎসগুলো চিহ্নিত করে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।
আমরা হয়তো সবাই জানি না বাংলাদেশে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স ঠেকাতে আইন রয়েছে। বাংলাদেশে ‘ওষুধ আইন ২০২২’-এ অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং প্রেসক্রিপশন ছাড়া বিক্রি নিয়ন্ত্রণের বিধান রয়েছে। এই আইনে চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।
তাহলে আইন মানা হয় না কেন?
ফার্মেসি মালিক ও সাধারণ জনগণের মধ্যে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স সম্পর্কে জ্ঞান এবং সচেতনতার অভাব, সামান্য অসুস্থতায় ডাক্তারের কাছে না গিয়ে সরাসরি ফার্মেসি থেকে ওষুধ কেনার প্রবণতা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে নিয়মিত ও কঠোর তদারকি ও শাস্তির অভাব উল্লেখযোগ্য কারণ।
তবে সমস্যার কিন্তু সমাধানও রয়েছে। প্রতিটি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে অ্যান্টিবায়োটিক স্টুয়ার্ডশিপ প্রোগ্রাম বাধ্যতামূলক করা এবং চিকিৎসার সিদ্ধান্তকে ল্যাবরেটরি ডেটা (অ্যান্টিবায়োগ্রাম) দ্বারা পরিচালিত করা, অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের বিপদ সম্পর্কে জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক প্রচার চালানো, প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি বন্ধ করতে আইন কঠোরভাবে কার্যকর করা এবং নিয়মিত নজরদারি করা।
সব স্টেকহোল্ডারদের (চিকিৎসক, পশু চিকিৎসক, কৃষক, পরিবেশবিদ) নিয়ে একটি কার্যকর ও সমন্বিত ওয়ান হেলথ কৌশল তৈরি করা জরুরি। অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সের বিরুদ্ধে লড়াইটি দীর্ঘমেয়াদি। এই সমস্যা মোকাবিলায় গবেষণা, নীতিমালা ও সর্বোপরি ব্যক্তিগত সচেতনতা অপরিহার্য।
ডা. কাকলী হালদার : এমবিবিএস, এমডি (মাইক্রোবায়োলজি), সহকারী অধ্যাপক, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ
সম্পর্কিত বিষয়:
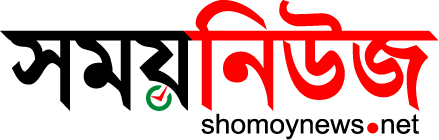



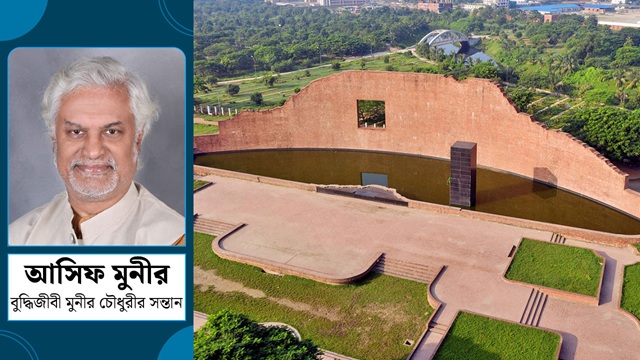

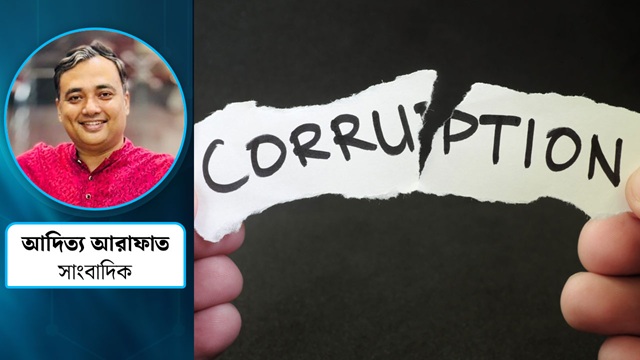



আপনার মূল্যবান মতামত দিন: