ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিক ও তার বিপুল সৃষ্টিজগৎ
প্রকাশিত:
৪ অক্টোবর ২০২৫ ১১:২৯
আপডেট:
৯ জানুয়ারী ২০২৬ ০২:৩৬
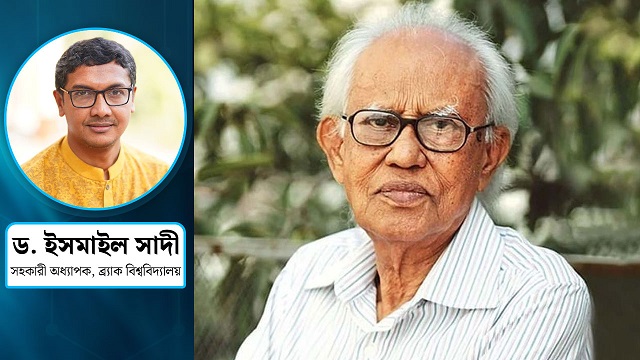
আহমদ রফিক নামটির সঙ্গে 'ভাষাসংগ্রামী' শব্দবন্ধ একাত্ম হিসেবে উচ্চারিত হয়ে আসছে ছয়-সাত দশক ধরে। পাশাপাশি রবীন্দ্রসাহিত্যের গবেষক হিসেবেও তিনি সমান খ্যাতিমান। তিনি শারীরিকভাবে আর আমাদের মাঝে নেই। ২ অক্টোবর রাত ১০টা ১২ মিনিটে তিনি প্রয়াত হয়েছেন।
তিনি বেঁচে থাকবেন তাঁর বিচিত্র সৃষ্টিকর্মের মধ্যে। যে জীবন তিনি কাটিয়েছেন, তাতে তিনি সন্তুষ্টই ছিলেন; কোনো খেদ ছিল না। ভাষা আন্দোলনে অংশ নেওয়া আরও অনেকেই দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন। তাদের মধ্যে অনেকে নিজস্ব সফল পেশাজীবন কাটিয়ে গেছেন। কিন্তু আহমদ রফিক পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন লেখালেখির মতো 'অনিশ্চিত ও কণ্টকাকীর্ণ পথকে'।
তার সহযোদ্ধাদের আর তেমন কেউ জীবন নিয়ে এতটা ঝুঁকি নেননি। তাই কেবল ভাষাসংগ্রামী খ্যাতির মধ্যেই আহমদ রফিকের জীবন সীমায়িত নয়, তার জীবনকে মূল্যায়ন করতে গেলে অবধারিতভাবে আমাদের প্রবেশ করতে হবে তার সাত দশক ধরে তিলে তিলে গড়ে তোলা সৃজনশীল ভুবনের অভ্যন্তরে।
কী আছে সেই ভুবনে কিংবা কী নেই তার সেই সৃষ্টিশীল ভুবনে—এই প্রশ্ন বিবেচনায় নিয়ে করতে হবে তত্ত্বতালাশ। কেননা, আহমদ রফিককে মূল্যায়ন করতে হলে তার রচিত শতাধিক গ্রন্থকে গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক। তার মতো সৃষ্টিশীল ব্যক্তিকে মূল্যায়ন করতে তার রচিত বিচিত্র গ্রন্থ, রচিত বিপুল চিন্তাশীল প্রবন্ধ-নিবন্ধকে বিবেচনায় নেওয়াটাই শ্রেয়তর।
আহমদ রফিক জন্মগ্রহণ করেন ১৯২৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। মাত্র কিছু দিন আগে তিনি ৯৬ বছর পূর্ণ করেছিলেন। এক জীবনে ভাষা আন্দোলনের সংগঠক হিসেবে যার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে, তার জীবনের জন্য একধরনের গর্ব তো থাকতেই পারে।
জীবনে ও সৃজনে, চিন্তা ও যাপনে তিনি যেভাবে সময়কে বশ মানিয়ে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণায় অবদান রেখে গেছেন, তাতে ব্যক্তি আহমদ রফিক অলক্ষ্যে এক অনন্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে গেছেন। সেই প্রতিষ্ঠানের জ্ঞাননিষ্ঠ সাগরে আমরা প্রতিনিয়ত স্নাত হই।
নিজের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য ও চিন্তা প্রসারে তিনি রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্র (১৯৮৯) নামে একটি ট্রাস্ট গড়ে তুলেছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বাংলাদেশ ও ভারতে সফল সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন তিনি। সেই সময় রবীন্দ্রসাহিত্য-বিষয়ক আয়োজনের কারণে নতুন প্রজন্মের মাঝে রবীন্দ্রসাহিত্যের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছিল। নতুন প্রজন্মের একঝাঁক তরুণ-তরুণী এই উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। যাদের অনেকেই আজ খ্যাতিমান অধ্যাপক-লেখক-গবেষক।
আহমদ রফিকের সৃজনসত্তায় আমরা প্রধানত পাই একজন মননশীল লেখককে, ভাষা আন্দোলন-বিষয়ক নৈর্ব্যক্তিক গবেষককে (যেখানে নিজের অবদান সচেতনভাবে উহ্য রেখেছেন), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য-বিষয়ক মৌলিক গ্রন্থপ্রণেতা ও কবিকে। উপরন্তু ইতিহাসচর্চাকারী, সমাজ-রাজনীতির নৈর্ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণকারী হিসেবে তিনি নিজেকে অনন্য উচ্চতায় আসীন করেছেন।
অন্যদিকে নজরুল-জীবনানন্দের পাশাপাশি ত্রিশের কবি বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দীনেশ দাস, তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম নায়ক ইলা মিত্র, বিপ্লবের বরপুত্র চে গুয়েভারাকে নিয়েও রয়েছে তার নিজস্ব মূল্যায়ন। বাংলাদেশের কবিতার মূল্যায়ন ও সমালোচনায় তার নিজস্ব ও ঋদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি অনেক অ্যাকাডেমিশিয়ানের কাজকে সহজ করে দিয়েছে।
ব্যক্তিজীবনে পূর্ণকালীন লেখক আহমদ রফিকের নিরন্তর গবেষণা ও নতুন নতুন পর্যবেক্ষণ ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাংলা সাহিত্য সমালোচনার নতুন নতুন দিগন্তকে উন্মোচন করেছে। এত কিছুর পরও তার চলনে-বলনে আত্মগর্বী হওয়া কিংবা আত্মতুষ্টি লাভ করা কিংবা গরিমা প্রকাশ অথবা অনেকের মতো কাউকে বাতিল করার মতো বাতুলতা তিনি কখনো দেখাননি। ব্যক্তি আহমদ রফিকের এ এক বিশেষত্ব।
তিনি বিশ্বাস করতেন, ঘটনাই মানুষের জীবনকে পরিচালিত করে। তিনি যুক্তি দিয়েছেন, তা না হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নের সুযোগ পাওয়া আহমদ রফিককে কেন কেবল আবাসিকতার সুযোগ গ্রহণের সুবিধার্থে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে হবে? তিনি মনে করেন, যোগ্যতা এবং শর্ত পূরণ করা সত্ত্বেও তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আবাসিকতা না দিয়ে অন্যায় করেছিল। এজন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি একধরনের অভিমান লালন করেছেন তিনি।
তিনি মনে করেছেন, এখান থেকে তার জীবনের মোড় উল্টোদিকে ঘুরে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ পেলে রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে আরও তৎপর থাকার পাশাপাশি মেধাবী শিক্ষার্থী হিসেবে অধ্যাপনা করার সুযোগও হয়তো তিনি পেতেন; যেটা চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়নের কারণে হয়নি।
অন্যদিকে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার 'অপরাধে' ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র হিসেবে কেবল তারই ছাত্রজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, তার জীবনকে অনিশ্চিত করে তোলে। কারণ, স্নাতক সম্পন্ন করতে পারলেও তিনি চিকিৎসাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার সুযোগ পাননি। ফলে ব্যক্তিজীবনে মার্ক্সবাদী চিন্তার অনুসারী আহমদ রফিককে লেখালেখিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে হয়। লেখালেখিতেও তিনি তার রাজনীতি-সঞ্জাত চিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।
তিনি যেসব বিষয়ে হাত দিয়েছেন, সেখানেই হয়ে উঠেছেন সেই বিষয়ের বিশারদ। রচনার ব্যাপকতার ওপর ভিত্তি করে তার বিচিত্র সাধনার ক্ষেত্রকে মোটা দাগে সাতটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।
- এক. ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা,
- দুই. রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্য গবেষণা,
- তিন. সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতি-বিষয়ক পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা,
- চার. সাহিত্য সমালোচনা,
- পাঁচ. কবিতা ও শিশুসাহিত্য,
- ছয়. আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ রচনা,
- সাত. পত্রিকা ও গ্রন্থ সম্পাদনা।
সাতচল্লিশের দেশভাগকে তিনি বলেছেন, একটা ‘নিবার্য’ বিষয়কে রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার কারণে অনিবার্য তোলা হয়েছিল। বাল্যকালে তৎকালীন মুসলিম লীগের কার্যক্রম তাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। বরং তাদের ডাকে সাড়া না দেওয়ায় হতে হয়েছিল নির্যাতনের শিকার।
কলেজ পড়ুয়া আহমদ রফিক ১৯৪৮ সালের মার্চে মুন্সিগঞ্জে থেকেই ভাষা আন্দোলনে প্রথম অংশগ্রহণ করেন। এরপর থেকে ঢাকাবাসী হন তিনি। ১৯৫০ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রথম ম্যাগাজিনে ‘সংকেত’ নামে কবিতা প্রকাশিত। মূলত তখন তিনি কবিতাই লিখতেন।
ভাষা আন্দোলনের প্রভাবে বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্যের যে নতুনত্বের আত্মপ্রকাশ ঘটে, তা প্রথমে ঘটে কবিতার মধ্য দিয়েই। এই সময়ে আবির্ভূত কবিগণই পরবর্তী সময়ে কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির পথকে দিক-নির্দেশনা প্রদান করে গেছেন; যে পথ এখনো চলমান।
কবিতার এই অগ্রযাত্রা দিয়ে সেই সময়ের কবিগণ আলোড়িত হলেও কবিদের আগেই প্রকাশিত হয় আহমদ রফিকের সাহিত্য সমালোচনামূলক গ্রন্থ শিল্প সংস্কৃতি জীবন (১৯৫৮)। এর মধ্য দিয়ে পঞ্চাশের দশকের বাংলাদেশের কোনো লেখকের প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং গ্রন্থকার হিসেবে তারও অগ্রযাত্রার শুরু হয়।
শুরু হয় তার আরেক লড়াই—বাংলাদেশের প্রবন্ধসাহিত্যকে নিজস্ব কাঠামোতে দাঁড় করানোর স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার পর সাহিত্যকে আলাদা মাত্রা দান করানোর এক নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন তিনি। ফলে তার হাত ধরেই শুরু হয়েছে অনেক প্রথমের।
যেমন ভাষা আন্দোলনে শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে প্রথম শহীদ মিনার স্থাপনের পরিকল্পনাকারীদের একজন ছিলেন তিনি, তেমনি ষাটের দশকের মাঝামাঝিতে নিজস্ব মেডিকেল পত্রিকা দ্য মেডিকেল ডাইজেস্ট, চিকিৎসা-বিজ্ঞান-বিষয়ক পরিভাষা প্রণয়ন উপলক্ষে ‘পরিভাষা’ সংকলন এবং বাংলা একাডেমি থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞান পরিভাষা কোষ প্রকাশিত হয় তার হাত ধরে।
১৯৭৭ সালে আহমদ রফিক রচিত প্রথম রবীন্দ্রসাহিত্য-বিষয়ক গ্রন্থ আরেক কালান্তরে দিয়েই বাংলা একাডেমি প্রকাশ করে তাদের রবীন্দ্রসাহিত্য-বিষয়ক বই। কুষ্টিয়া, শাহজাদপুরের পাশাপাশি নওগাঁর পতিসরেও ছিল রবীন্দ্র-কুঠিবাড়ি। তার রবীন্দ্রভুবনে পতিসর গ্রন্থ প্রকাশের আগে বাংলাদেশের খুব কম মানুষের কাছেই তা পরিচিত ছিল।
এভাবে পদ্মাপারের সেই গাল্পিক জাদুকর, ছোটগল্পের শিল্পরূপ: পদ্মাপর্বের রবীন্দ্রগল্প, রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা ও বাংলাদেশ, রবীন্দ্রভাবনায় গ্রাম: কৃষি ও কৃষক, রবীন্দ্রসাহিত্যের নায়িকারা দ্রোহে ও সমর্পণে প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করে তিনি একক প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রসাহিত্য-বিষয়ক সবচেয়ে বেশি গ্রন্থে রচয়িতা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।
ভাষা আন্দোলন বিষয়ে তার গ্রন্থও একক লেখক হিসেবে বোধ করে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি। ভাষা আন্দোলনের তাত্ত্বিক বিষয় তাকে সবচেয়ে আকৃষ্ট করেছে বলে নানামাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ আন্দোলন ও আন্দোলনের ইতিহাসকে পর্যবেক্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। যে কারণে তার গ্রন্থের নাম হয় ভাষা আন্দোলন: ইতিহাস ও তাৎপর্য, একুশের ইতিহাস আমাদের ইতিহাস, ভাষা আন্দোলন: ইতিহাস ও উত্তরপ্রভাব, একুশের মুহূর্তগুলো প্রভৃতি।
ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাসও তিনিই প্রথম রচনা করেছেন। এ বিষয়ক তার গ্রন্থের নাম ভাষা আন্দোলন: টেকনাফ একে তেঁতুলিয়া। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে রয়েছে তার অনবদ্য গ্রন্থ একাত্তর পাকবর্বরতার সংবাদভাষ্য, বাঙালির স্বাধীনতাযুদ্ধ, ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো, একুশ থেকে একাত্তর প্রভৃতি।
কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও সাহিত্যনির্ভর গ্রন্থ বাঙলা বাঙালি আধুনিকতা ও নজরুল গ্রন্থটি বেশ অভিনব প্রকল্প। এর পাশাপাশি তিনি নজরুলের সব্যসাচী প্রতিভা নিয়ে রচনা করেছেন নজরুল প্রতিভার নানা মাত্রা।
যারা আহমদ রফিকের সান্নিধ্য লাভ করেছেন, তারা জানেন, দেশভাগের সময়কার দেশান্তরি হওয়ার যন্ত্রণা তিনি নিজের বেদনা হিসেবে লালন করেছেন। কারণ তিনিও বন্ধু হারিয়েছিলেন। দেশভাগকে তিনি রাজনৈতিক নেতৃত্বে হঠকারিতা হিসেবে দেখেছেন। ত্রিকালদর্শী এই লেখক তাই পঁচাশি বছর বয়সে রচনা করেন বিশাল কলেবরের বই দেশবিভাগ: ফিরে দেখা (২০১৪)।
বইটি পাঠক-গবেষক-অ্যাকডেমিশিয়ানদের কাছে ইতিমধ্যে আদৃত হয়েছে। এরই বাইরে বাংলাদেশে কবিতা-বিষয়ক সমালোচনামূলক গ্রন্থ কবিতা আধুনিকতা ও বাংলাদেশের কবিতা, বাংলাদেশের কবিতা: দশকভাঙা বিচার, কবিতার বিচিত্র ভাষ্য তার সাহিত্য ও কবিতা-বিষয়ক সাম্প্রতিক ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে উদ্ভাসিত করে।
এছাড়া বিষ্ণু দে: কবি ও কবিতা, জীবনানন্দ: কবি প্রেমিক ও গৃহী, মৃত্যুহীন বিপ্লবী চে গুয়েভারা, ইলা-রমেন কথা: প্রাসঙ্গিক রাজনীতি প্রভৃতি তার অত্যন্ত শ্রমসাধ্য গ্রন্থ। কারণ, গ্রন্থগুলো পাঠ করলে মনে হয় একজন অ্যাকাডেমিশিয়ান তার সন্বিষ্ঠ দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে ক্রমাগত সাধনা করে গেছেন।
তার ভাষার লড়াই যেন সাহিত্য ও সংস্কৃতির বৃহত্তর লড়াইয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে গেছে। তাই আহমদ রফিককে দেখতে হবে তার বিপুল সৃষ্টিকর্ম ও সাধনার মধ্য দিয়ে। তা না হলে দীর্ঘ জীবনে আপসহীন ব্যক্তিটির শিল্পচর্চার সাধনা কালের গহ্বরে হারিয়ে যাবে। আহমদ রফিকের এমন অনেক সৃষ্টিকর্ম রয়েছে, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চিন্তার খোরাক জোগাবে। তার সৃষ্টিকর্ম প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের মাঝে প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকুক, চর্চিত হোক তার সমাজ-সংস্কৃতির বহুকৌণিক দৃষ্টিভঙ্গি, সেটাই প্রত্যাশা।
ড. ইসমাইল সাদী : সহকারী অধ্যাপক, স্কুল অব জেনারেল এডুকেশন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
সম্পর্কিত বিষয়:
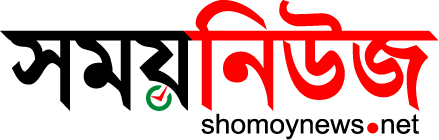



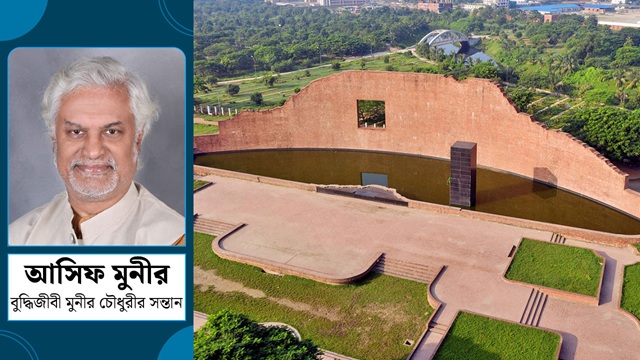

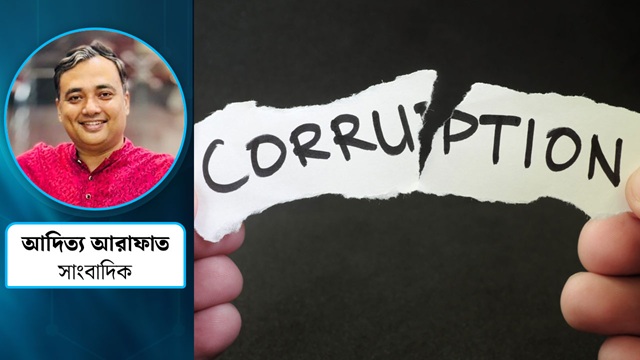




আপনার মূল্যবান মতামত দিন: