দুর্নীতিবিরোধী সংবাদ প্রচারে উন্নত দেশগুলো যে পদক্ষেপ নেয়
প্রকাশিত:
৩০ এপ্রিল ২০২৫ ০০:৪৬
আপডেট:
৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ২১:০৩
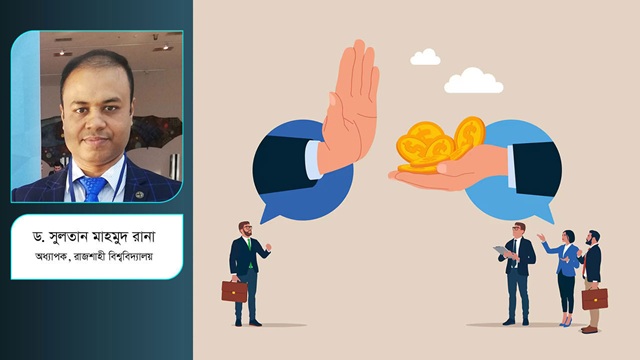
দুর্নীতি বিশ্বের প্রায় সব দেশেই কোনো না কোনোভাবে বিদ্যমান। কোনো রাষ্ট্রে এর মাত্রা অনেক বেশি, আবার কোনো রাষ্ট্রে কম। উন্নত অনেক রাষ্ট্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। ওইসব দেশ দুর্নীতি প্রতিরোধে যে কৌশলগুলো গ্রহণ করেছে, তার একটি প্রধান দিক হলো তথ্য প্রবাহের স্বচ্ছতা এবং নাগরিকের দ্রুত সচেতনতা।
দুর্নীতির খবর জনগণের কাছে দ্রুত ও সহজে পৌঁছানোর কারণেই এসব দেশে প্রশাসনের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দুর্নীতি তুলনামূলকভাবে কম হচ্ছে। দুর্নীতিবিরোধী সংবাদ প্রচারের জন্য শুধু সাংবাদিকতার স্বাধীনতাই যথেষ্ট নয়—প্রয়োজন আইনি কাঠামো, প্রযুক্তিগত সুরক্ষা এবং সামাজিক সচেতনতা।
সঠিক সময়ে দুর্নীতিবিরোধী খবর প্রচার করতে উন্নত দেশগুলো কঠোর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, আইনি সুরক্ষা এবং নৈতিক সাংবাদিকতার নীতিমালা অনুসরণ করে। এ কারণে আমরা লক্ষ করেছি যে, গণমাধ্যম কিংবা সংবাদপত্র উন্নত দেশে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরক্ষা লাইন। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের "The Washington Post" বা যুক্তরাজ্যের "The Guardian" দুর্নীতির খবর প্রকাশে সাহসিকতার পরিচয় দেয়।
১৯৭০-এর দশকে ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির ঘটনা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ, যেখানে সাংবাদিকরা প্রেসিডেন্ট নিক্সনের দুর্নীতিমূলক কর্মকাণ্ড প্রকাশ করে পুরো দেশকে নাড়িয়ে দেয়। গণমাধ্যমের সাথে দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত গবেষণা করতে গিয়ে জেনিফার ব্রাউন বলেন, ‘গণমাধ্যমে দুর্নীতির খবর প্রকাশ হলে, তা সমাজের মানুষের মধ্যে এক ধরনের চাপ সৃষ্টি করে এবং রাজনৈতিক নেতা বা কর্মকর্তাদের ওপর জনগণের প্রভাব বাড়ায়, যা দুর্নীতি রোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।’
সরকারি-বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠানের তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত, যা সাংবাদিকদের দুর্নীতি অনুসন্ধানে সহায়তা করে। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের Freedom of Information Act (FOIA) বা সুইডেনের স্বচ্ছ প্রশাসনিক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা সাধারণ নাগরিক বা সাংবাদিকরা সরকারি নথিপত্র দেখতে এবং বিশ্লেষণ করতে পারেন।
কানাডা বা সুইডেনের মতো দেশে, সরকার বাধ্য থাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তথ্য প্রকাশ করতে। এতে সরকারি কর্মকাণ্ডের ওপর জনগণের নজরদারি সহজ হয়। এমনকি দুর্নীতির তথ্য ফাঁসকারী ব্যক্তিদের (Whistleblowers) সুরক্ষা দেওয়া হয় কঠোর আইনের মাধ্যমে।
ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হুইসলব্লোয়ারদের আইনি সহায়তা, গোপনীয়তা এবং চাকরিচ্যুতির হাত থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা রয়েছে। অ্যান্টি-করাপশন থিওরি অনুযায়ী, যেকোনো দুর্নীতির ঘটনা যদি জনসাধারণের কাছে ত্বরিত সময়ে পৌঁছায়, তাহলে সেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব।
গবেষক ড. রিচার্ড রিচার্ডসনের মতে, ‘যত বেশি সময় ধরা পড়ে না, তত বেশি দুর্নীতি বিস্তার লাভ করে।’ ওইসব দেশের কার্যকরী উদাহরণ যেখানে গণমাধ্যম ও জনগণ দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার, তারা দ্রুত সরকারের শুদ্ধতার পথে চলে এসেছে। যেমন, দক্ষিণ কোরিয়ার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে।
দুর্নীতির গভীরে যাওয়ার জন্য উন্নত দেশগুলোতে বিশেষায়িত অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ইউনিট গঠন করা হয় (যেমন—ব্রিটেনের BBC Panorama বা জার্মানির Der Spiegel)। এগুলোয় প্রশিক্ষিত সাংবাদিক, ডেটা অ্যানালিস্ট এবং আইনি বিশেষজ্ঞরা কাজ করেন। সাংবাদিকদের সাইবার হামলা ও ফাঁস হওয়া থেকে রক্ষা করতে উন্নত দেশগুলো এনক্রিপশন টুলস (Signal, SecureDrop) ব্যবহার করে।
নরওয়ে ও নেদারল্যান্ডসে সাংবাদিকদের ডিজিটাল সিকিউরিটি প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক। ফিনল্যান্ড বা ডেনমার্কের মতো দেশে মিডিয়া নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলো সরকার থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন। দুর্নীতির খবর প্রকাশে বাধা দেওয়া হলে সংবাদমাধ্যম তাৎক্ষণিকভাবে আদালতের শরণাপন্ন হতে পারে।
দুর্নীতি প্রতিরোধে স্বচ্ছতা বা ট্রান্সপারেন্সি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ভিত্তি। এই থিওরি অনুযায়ী, যত বেশি সরকারি কার্যক্রমের তথ্য জনগণের কাছে উন্মুক্ত থাকবে, তত বেশি সরকারি কর্মচারী দুর্নীতির বিরুদ্ধে সতর্ক থাকবে। Transparency International এর প্রতিবেদনে (২০২৩) বলা হয়েছে, তথ্যের সহজ প্রবাহ ও সরকারের স্বচ্ছতা মানুষের আস্থা বাড়ায়, যা দুর্নীতির সুযোগ কমিয়ে দেয়।
সুইডেনের মতো দেশে ট্রান্সপারেন্সি লেজিসলেশন বা তথ্যের অধিকারের আইন দুর্নীতি দমনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। রাষ্ট্রের সব তথ্য নাগরিকদের জন্য উন্মুক্ত থাকে এবং এর মাধ্যমে দুর্নীতির ঘটনার প্রমাণ পেলে তা দ্রুত জনগণের কাছে পৌঁছে যায়।
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং তথ্য প্রকাশ দুটোই দুর্নীতি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নাগরিকদের কাছে তথ্য পৌঁছালে তারা সরকারের ওপর সঠিকভাবে নজরদারি রাখতে পারে। তাত্ত্বিকভাবে, জনগণের অংশগ্রহণ এবং কর্তৃপক্ষের ওপর জনবিচার দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার গবেষক সিলভিয়া মেন্ডোজা একে 'পাবলিক চেক' হিসেবে চিহ্নিত করেন, যা জনগণের অবাধ তথ্যপ্রবাহের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
বিশেষজ্ঞরা যেমন বলছেন, ‘যদি জনগণের কাছে সরকারি কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হয়, তবে দুর্নীতির ঘটনা চিহ্নিত করা সহজ হয় এবং প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।’
দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বাড়াতে উন্নত দেশগুলো নাগরিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করে। স্কুল-কলেজে নৈতিকতা ও সুশাসন সম্পর্কিত কোর্স অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কেবল মিডিয়া নয়, উন্নত দেশগুলোতে দুর্নীতির তদন্তে স্বাধীন এন্টি-করাপশন কমিশন, বিচার বিভাগ এবং সিভিল সোসাইটি একত্রে কাজ করে। ফলে খবর দ্রুত প্রকাশ পায় এবং ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
উন্নত দেশে সংবাদপত্র, টেলিভিশন ও অনলাইন মিডিয়াতে ‘investigative journalism’ (তদন্তমূলক সাংবাদিকতা) বিশেষভাবে সক্রিয় থাকে। উন্নত দেশগুলোয় দুর্নীতির তদন্ত ও প্রতিরোধের জন্য বিশেষ সংস্থা রয়েছে — যেমন যুক্তরাষ্ট্রে FBI-এর Public Corruption Unit। যুক্তরাজ্যে Serious Fraud Office (SFO)। অস্ট্রেলিয়ায় Independent Commission Against Corruption (ICAC)। এসব সংস্থা অভিযোগ আসার সঙ্গে সঙ্গে নিরপেক্ষ তদন্ত শুরু করে এবং জনসাধারণকে অগ্রগতির বিষয়ে নিয়মিত আপডেট দেয়।
বিভিন্ন দেশে দুর্নীতির খবর প্রচারে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়মিত নিরীক্ষার (audit) আওতায় আনা হয়। নিরীক্ষার ফলাফল সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, যাতে গোপন দুর্নীতি লুকিয়ে রাখা না যায়। অনেক উন্নত দেশে দুর্নীতির খবর ও প্রমাণ জমা দেওয়ার জন্য অনলাইন প্ল্যাটফর্ম বা অ্যাপ চালু আছে, যেমন কানাডায় "Integrity Portal", ইউরোপীয় ইউনিয়নের "EU Whistleblower Channel"।
এই মাধ্যমগুলো গোপনীয়তা নিশ্চিত করে, যাতে সাধারণ মানুষও নিরাপদে দুর্নীতির তথ্য দিতে পারে। এমনকি এসব দেশে বিভিন্ন কার্যকরী পদ্ধতিগুলোর ফলে দুর্নীতির ঘটনা চাপা পড়ে না এবং দ্রুত জনসমক্ষে আসে। কোনো কোনো দেশে একটি নিরপেক্ষ, স্বাধীন এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, যা সরকার বা রাজনীতিকদের প্রভাবমুক্ত হয়ে দুর্নীতির তদন্ত করে। হংকং – Independent Commission Against Corruption (ICAC) (১৯৭৪ সালে গঠিত)। ICAC গঠনের পর মাত্র ১০ বছরে হংকংয়ের পুলিশবাহিনীতে দুর্নীতির হার নাটকীয়ভাবে কমে যায়।
সিঙ্গাপুরে Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের অধীনে সরাসরি, ফলে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ নেই। প্রতিটি সরকারি সংস্থাকে তাদের ব্যয়, সিদ্ধান্ত, নীতিমালা ও চুক্তি জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হয়। জনগণ চাইলে তথ্য চাইতে পারে। নরওয়ে—সব সরকারি ক্রয় ও নিয়োগ তথ্য Public Procurement Portal-এ উন্মুক্ত। ফিনল্যান্ডে আমলাদের সম্পদের হিসাব জনগণের জন্য উন্মুক্ত থাকে।
বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাখা হয়। দুর্নীতির মামলায় দ্রুত ও কঠোর বিচার হয়। তাছাড়া এসব দেশে বিচার বিভাগ সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ। যুক্তরাজ্যে The Bribery Act, 2010 অনুযায়ী ঘুষের অভিযোগে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়। জার্মানিতে আদালত নিজস্ব উদ্যোগে (Suo Moto) দুর্নীতির তদন্ত শুরু করতে পারে।
এমনকি ওইসব দেশসমূহে সরকারি আর্থিক কর্মকাণ্ড, বড় প্রকল্প এবং উন্নয়ন কাজের ওপর নিয়মিত ও কঠোর নিরীক্ষা হয়। কানাডাতে Office of the Auditor General স্বাধীনভাবে প্রতিবছর সরকারের ব্যয় ও নীতি পর্যালোচনা করে। নিউজিল্যান্ডে Integrity institutions, যেমন Auditor-General এবং Ombudsman, অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা রাখে।
এছাড়াও সরকারি সেবা অনলাইনে এনে সরাসরি জনগণের কাছে পৌঁছানো হয়—যাতে দালাল বা অবৈধ লেনদেনের সুযোগ কমে। এস্তোনিয়ায় বিশ্বের সবচেয়ে ডিজিটাল সরকার। জন্ম নিবন্ধন থেকে ট্যাক্স ফাইলিং পর্যন্ত সব কিছু অনলাইনে। ডেনমার্কে ৯৮ শতাংশ সরকারি সেবা ডিজিটাল মাধ্যমে হয়, তাই ঘুষ দেওয়ার অবকাশ নেই।
এছাড়াও, উন্নত দেশে জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা ও সক্রিয়তা অত্যন্ত উঁচু মানের। জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর কঠোর নজর রাখে, নিয়মিত গণমাধ্যম অনুসরণ করে এবং দুর্নীতির অভিযোগ এলে দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখায়। ফলে, নেতৃবৃন্দও নিজেদের স্বচ্ছ রাখতে সচেষ্ট থাকেন।
সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখা যায়, প্রকাশিত দুর্নীতি তথ্য সামাজিক মানদণ্ড এবং সরকারের শুদ্ধতার প্রতি জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে সহায়তা করে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, "যত বেশি দুর্নীতির ঘটনা প্রকাশ পাবে, তত বেশি জনগণ সেগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে এবং এটি প্রশাসনের দুর্নীতির প্রতি অস্থিরতা তৈরি করবে।"
সার্বিক বিশ্লেষণে বলা যায় যে, দুর্নীতির তথ্য প্রকাশ এবং জনগণের কাছে দ্রুত সেই তথ্য পৌঁছানো একদম অপরিহার্য। ট্রান্সপারেন্সি, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, হুইসলব্লোয়ার সুরক্ষা এবং পাবলিক চেকস অ্যান্ড ব্যাল্যান্স-এর মত তাত্ত্বিক ধারণাগুলো দুর্নীতি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।
যত বেশি তথ্য প্রকাশ এবং জনগণের অংশগ্রহণ থাকবে, তত বেশি দুর্নীতি মোকাবিলা করা সম্ভব। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো যদি এসব নীতির কিছু অংশ বাস্তবায়ন করতে পারে, তবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে পারে।
ড. সুলতান মাহমুদ রানা ।। অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
[email protected]
সম্পর্কিত বিষয়:



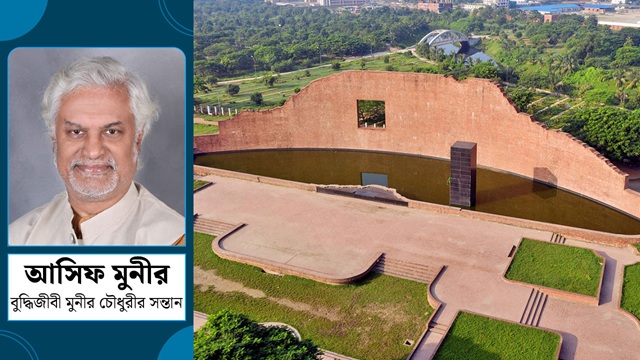

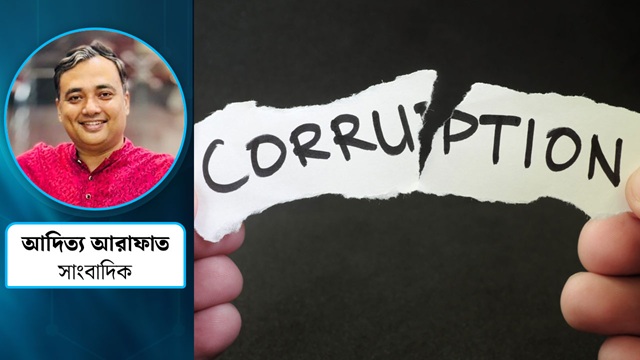



আপনার মূল্যবান মতামত দিন: