ফার্মেসি শিক্ষাকে কীভাবে আরও আধুনিক করা যায়
প্রকাশিত:
২৭ জানুয়ারী ২০২৫ ২৩:২৩
আপডেট:
৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ০০:৪৬

বাংলাদেশে ফার্মেসি শিক্ষার সূচনা হয় ১৯৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছরের বিফার্ম (সম্মান) কোর্স চালু করার মাধ্যমে। এরপর ১৯৮৫ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯৯০ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্মেসিতে স্নাতক কোর্স চালু হয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ১৯৯৪ সালে ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, চট্টগ্রাম এবং ১৯৯৬ সালে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে ফার্মেসি বিভাগের যাত্রা শুরু হয়।
শুরু থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তিচ্ছুদের পছন্দের শীর্ষে অবস্থান করতো ফার্মেসি এবং এখনো পরিস্থিতির তেমন পরিবর্তন হয়নি। চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে সব শীর্ষ সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্মেসি বিভাগ চালু করার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ফলাফল হলো বর্তমানে ১৩টি সরকারি ও ৩০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্মেসিতে চার অথবা পাঁচ বছরের বিফার্ম কোর্স চালু আছে।
সরকারি বেসরকারি সব বিশ্ববিদ্যালয় মিলিয়ে ফার্মেসিতে চার বছরের বিফার্ম (সম্মান) এবং পাঁচ বছরের বিফার্ম (প্রফেশনাল) কোর্সে ফার্মেসি কাউন্সিল অনুমোদিত আসন সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার।
১৫ বছরে দেশে ফার্মেসি পড়ানো হয় এমন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনি রেজিস্টার্ড ফার্মাসিস্টের সংখ্যাও হু হু করে বেড়েছে। বর্তমান পদ্ধতিতে ফার্মেসি গ্র্যাজুয়েটরা তাদের বিফার্ম সনদের কপি ফার্মেসি কাউন্সিলে জমা দিলে, ফার্মেসি কাউন্সিল নিবন্ধনের জন্য কোনো পরীক্ষা ছাড়াই এ-গ্রেড রেজিস্ট্রেশন প্রদান করে।
২০০৬-২০০৭ সালের দিকে নিবন্ধনের জন্য পরীক্ষা পদ্ধতি চালু হলেও পরে সেটি বিভিন্ন কারণে টিকে থাকেনি। ফলে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যত সংখ্যক ফার্মেসি গ্র্যাজুয়েট তৈরি করে তাদের সবাই ফার্মেসি কাউন্সিলের এ-গ্রেড রেজিস্ট্রেশন পেয়ে যান। উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে ফার্মেসি কাউন্সিল নিবন্ধিত স্নাতক ফার্মাসিস্টের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩ হাজার। ফার্মেসি কাউন্সিলের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে নিবন্ধিত স্নাতক ফার্মাসিস্টের সংখ্যা ২১ হাজারেরও বেশি।
অর্থাৎ, ১৫ বছরে এ-গ্রেড ফার্মাসিস্ট (স্নাতক ফার্মাসিস্ট) হিসেবে নিবন্ধন পেয়েছেন প্রায় ১৮ হাজার ফার্মাসিস্ট। সম্প্রতি আরও দুটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মেসি কোর্স চালু করেছে এবং রেজিস্ট্রেশন প্রদানের এ পদ্ধতি অব্যাহত থাকলে আগামী ২৫ বছরে দেশে রেজিস্টার্ড স্নাতক ফার্মাসিস্টের সংখ্যা দাঁড়াবে ৭০ হাজারের কাছাকাছি।
বাংলাদেশে ফার্মেসি শিক্ষা ও পেশাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য ফার্মেসি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার জন্য তৎকালীন সরকার ১৯৭৬ সালে ‘ফার্মেসি অধ্যাদেশ’ প্রণয়ন করে। অধ্যাদেশ অনুযায়ী কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্মেসিতে স্নাতক কোর্স চালু করতে হলে ফার্মেসি কাউন্সিলের অনুমোদন নিতে হয়। পাশাপাশি লাগে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুমোদন। সব সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে ফার্মেসি কাউন্সিলের অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য নির্দিষ্ট অ্যাক্রেডিটেশন নীতিমালা অনুসরণ করতে হয়।
২০১০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্লিনিক্যাল বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে চার বছরের বিফার্ম (সম্মান) কোর্সকে পাঁচ বছরের বিফার্ম (প্রফেশনাল) কোর্সে উন্নীত করে। কিন্তু, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পূর্বের চার বছরের বিফার্ম (সম্মান) কোর্স বহাল রাখে। তবে, পাঁচ বছরের বিফার্ম প্রফেশনাল কোর্স চালুর উদ্দেশ্য কাজে আসেনি। পাঁচ বছরের কোর্সে শেষ বছরে অন্তত ছয় মাসের হাসপাতালে ইন্টার্নশিপের কথা থাকলেও তার বাস্তবায়ন অনেক চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়ে।
চার বছরের বিফার্ম ডিগ্রির পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উক্ত সেশন থেকে পাঁচ বছরের ডক্টর অব ফার্মেসি (ফার্ম. ডি.) ডিগ্রি প্রদান করবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিফার্ম গ্র্যাজুয়েটদের ২৫ শতাংশ একবছর অতিরিক্ত অধ্যয়ন করে এবং হাসপাতালে ক্লিনিক্যাল ট্রেনিং সম্পন্ন করে ডক্টর অব ফার্মেসি (ফার্ম. ডি.) ডিগ্রি পাবে। এর মাধ্যমে আমাদের দেশে প্রথমবারের মতো পাঁচ বছর মেয়াদি ফার্ম. ডি. ডিগ্রির সূচনা হতে যাচ্ছে।
দেশের কোনো সরকারি হাসপাতালে গ্রাজুয়েট ফার্মাসিস্টের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হসপিটাল ফার্মেসি বা ক্লিনিক্যাল ফার্মেসি সেবা চালু না থাকায় ফার্ম. ডি. কোর্সের জন্য বাধ্যতামূলক ক্লিনিক্যাল ট্রেনিং নিয়ে জটিলতা তৈরি হবে কিনা তা নিয়ে আশঙ্কা আছে। ফার্ম. ডি. একটি ক্লিনিক্যাল ডিগ্রি। হাসপাতালে উপযুক্ত ট্রেনিং না পেলে বিফার্ম প্রফেশনাল কোর্সের মতো ফার্ম. ডি. কোর্সের সফলতা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে।
দেশে বছরে বছরে ফার্মেসি বিভাগের সংখ্যা বেড়েছে, ফার্মাসিস্টের সংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু একই সঙ্গে আমাদের দেশের ফার্মেসি শিক্ষা ও পেশার ধরনের সাথে উন্নত বিশ্বসহ পার্শ্ববর্তী অনেক দেশের সাথে আমাদের ফার্মেসি শিক্ষা ও পেশার ধরনে দূরত্ব বেড়েছে। ফার্মেসি একটি প্রফেশনাল বিষয়। প্রফেশনাল বিষয়ে পাঠদান একটি আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড মেনে করতে হয়। সারা বিশ্বে দিনে দিনে ফার্মেসি শিক্ষা ও পেশার যে পরিবর্তন হয়েছে, তার সাথে আমরা তাল মিলিয়ে চলতে পারিনি। এর অনেকগুলো কারণ রয়েছে। আমার লেখার উদ্দেশ্য এ বিষয়টি পরিষ্কার করা এবং করণীয় নির্ধারণ করা।
ফার্মেসি হলো স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা, যেখানে ওষুধের আবিষ্কার, উৎপাদন, প্রস্তুতকরণ, বিপণন, বিতরণ এবং ব্যবহারের নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা ও চর্চা করা হয়। ফার্মেসি শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো রোগীদের জন্য নিরাপদ, কার্যকর এবং সাশ্রয়ী ওষুধের ব্যবহার নিশ্চিত করা। আধুনিক ফার্মেসি শিক্ষার সূচনা হয় যুক্তরাষ্ট্রে। ১৯৩২ সালে যুক্তরাষ্ট্রে চার বছরের ব্যাচেলর ডিগ্রি ফার্মেসি প্র্যাকটিসের মানদণ্ড হিসেবে গৃহীত হয়। পরে আরও ব্যবহারিক শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ১৯৫০-এর দশকে পাঁচ বছরের ডিগ্রি চালু হয়।
শুরুর দিকে ফার্মেসি শিক্ষা ছিল পণ্যকেন্দ্রিক। এরপর যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৮০-এর দশকে ডক্টর অব ফার্মেসি (ফার্ম. ডি.) ডিগ্রি চালু হয়, যা ছয় বছর মেয়াদি এবং ক্লিনিক্যাল প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এটি রোগীকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে প্রায় সব দেশেই ফার্ম. ডি. ধীরে ধীরে ফার্মাসিস্টদের জন্য প্রাথমিক পেশাগত ডিগ্রি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, পাকিস্তান ও নেপালে অনেক আগেই পাঁচ থেকে ছয় বছরের ফার্ম. ডি. ডিগ্রি চালু হয়েছে।
উন্নত বিশ্বে ফার্মেসি শিক্ষার কাঠামো এবং পদ্ধতি এখন অত্যন্ত আধুনিক, বহুমুখী এবং রোগীকেন্দ্রিক। শিক্ষার্থীরা হাসপাতাল এবং কমিউনিটি ফার্মেসিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ পায়, যা রোগীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে দক্ষ করে তোলে। আধুনিক ফার্মেসি শিক্ষার আরেকটি বিশেষ দিক হলো আন্তঃপেশাগত শিক্ষা (Interprofessional Education)।
এখানে ফার্মাসিস্টদের ডাক্তার, নার্স এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে যৌথভাবে কাজ করার পদ্ধতি শেখানো হয়। তাছাড়া, উন্নত দেশে ফার্মেসির শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন অনকোলজি, নিউক্লিয়ার ফার্মেসি, পেডিয়াট্রিক ফার্মেসিতে বিশেষায়নের সুযোগ পান।
১৯৬০-এর দশকে যখন বাংলাদেশে ফার্মেসি শিক্ষা ও পেশার সূচনা হয়, সে একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে ফার্মেসি শিক্ষা ও পেশায় একটি ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। উক্ত দশকে ‘ক্লিনিক্যাল ফার্মেসি’র ধারণা চালু হয় এবং ফার্মাসিস্টদের ভূমিকা ওষুধ বিতরণের বাইরে সরাসরি রোগীর যত্ন প্রদান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। রোগীর চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা, ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ এবং পরামর্শ প্রদান ফার্মেসি শিক্ষার অন্যতম অংশ হয়ে ওঠে।
ফার্মাসিস্টরা ওষুধ উৎপাদন, মান নিয়ন্ত্রণ ও বিপণনের কাজ থেকে ধীরে ধীরে সরে আসতে শুরু করেন এবং ফার্মেসি শিক্ষা ও পেশা রোগীকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। এরপর, ১৯৭০-এর দশকে ‘ফার্মাসিউটিক্যাল কেয়ার’-এর ধারণা চালু হয়, যা রোগীদের ওষুধকেন্দ্রিক সেবাকে আরও সুসংহত করে। উন্নত বিশ্বে ফার্মেসি শিক্ষা ও পেশা এখন রোগীকেন্দ্রিক।
যুক্তরাষ্ট্রের ফার্মাসিস্টদের কাজের বর্তমান চিত্র দেখলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। যুক্তরাষ্ট্রে ফার্মাসিস্টদের প্রায় ৬০ শতাংশ কমিউনিটি ফার্মেসিতে এবং ৩০ শতাংশ ফার্মাসিস্ট হাসপাতাল ফার্মেসিতে কাজ করেন। সেখানকার মাত্র ৪ শতাংশ কাজ করেন ওষুধ কোম্পানিতে।
দেশে ফার্মেসি শিক্ষা ও পেশাকে ঢেলে সাজাতে হবে। উন্নত দেশের মতো প্রতি ৫০ বেডের হাসপাতালে অন্তত দুজন স্নাতক ফার্মাসিস্ট নিয়োগ দিতে হবে। এতে হাসপাতালে ওষুধের সঠিক ও যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত হবে, ডাক্তারদের ওপর চাপ কমবে, চিকিৎসা সেবার মান বাড়বে।
উন্নত দেশে স্নাতক ফার্মাসিস্ট ছাড়া ওষুধের দোকান খোলা বা চালানো অকল্পনীয়। দেশে এখন সেটি সম্ভব না হলেও ওষুধের দোকান খোলার জন্য বা চালানোর জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্ট নির্ধারণ করা উচিত। এতে ওষুধের অপব্যবহার ও ভুল ব্যবহার কমবে এবং রোগীদের ভালো ওষুধের প্রাপ্যতা নিশ্চিত হবে। আর ফার্মেসি শিক্ষাকে করতে হবে আন্তর্জাতিক মানের।
ইন্টারন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল ফেডারেশনের (এফআইপি) Global Competency Framework (GbCF) অনুযায়ী দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কারিকুলাম প্রণয়ন করতে হবে যা হবে রোগীকেন্দ্রিক। শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং অন্ততপক্ষে ছয় মাস থেকে এক বছর হাসপাতালে স্নাতক ফার্মাসিস্টদের তত্ত্বাবধানে ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা করতে হবে।
বর্তমানে দেশে যেহেতু ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে প্রচুর দক্ষ জনবলের দরকার সেহেতু সে চাহিদা পূরণের জন্য আলাদাভাবে ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্স বিভাগ চালু করা যেতে পারে, যার কারিকুলাম হবে ওষুধশিল্প ভিত্তিক। এতে ওষুধ শিল্প দক্ষ ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্টিস্ট পাবে, যারা ওষুধ আবিষ্কার ও উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। প্রসঙ্গত, ১৯৬০-এর দশক থেকে উন্নত বিশ্বে ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্স ও ফার্মেসি দুটি আলাদা ডিসিপ্লিনে বিভক্ত হয়ে গেছে।
মনে রাখতে হবে, ফার্মাসিস্ট ছাড়া পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা অসম্ভব। তাই, সব হাসপাতালে জরুরি ভিত্তিতে ফার্মাসিস্ট নিয়োগ দেওয়া অপরিহার্য। পাশাপাশি, ফার্মেসি কারিকুলামকেও ঢেলে সাজাতে হবে এবং রোগীকেন্দ্রিক কারিকুলাম তৈরি করতে হবে এবং ফার্মেসি শিক্ষার মান নিশ্চিতকরণে ফার্মেসি কাউন্সিলকে আরও জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে।
তা না হলে, দেশের মানুষ ফার্মাসিস্টদের সেবা থেকে বঞ্চিত হবে এবং অন্য দেশের সাথে আমাদের দেশের ফার্মেসি পেশা ও শিক্ষার ব্যবধান দিনে দিনে প্রকট হয়ে উঠবে। শুরু থেকেই ভুল ট্রেনে চলছে আমাদের ফার্মেসি শিক্ষা ও পেশা। একে সঠিক পথে নিয়ে আসতে হলে বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারকে একসাথে কাজ করতে হবে।
ড. মো. আজিজুর রহমান ।। অধ্যাপক, ফার্মেসি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
[email protected]
সম্পর্কিত বিষয়:



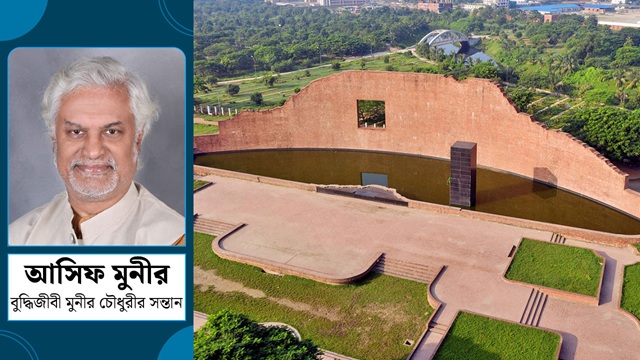

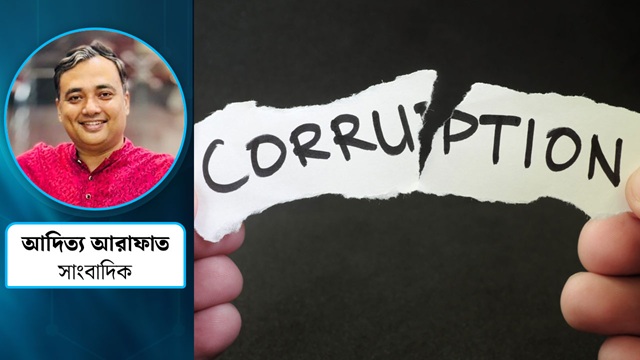



আপনার মূল্যবান মতামত দিন: