আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার আলোকে পুলিশ সংস্কার
প্রকাশিত:
২৪ জানুয়ারী ২০২৫ ২৩:১৯
আপডেট:
৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ০৪:৩৯

একটি দেশের মানুষের নিরাপত্তাবোধ সে দেশের সামগ্রিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বহুলাংশে প্রভাবিত করে। মানুষের প্রাত্যহিক জীবন কীভাবে চলবে তাও অনেকাংশে সে দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। আর মানুষের জীবনের জন্য অতি প্রয়োজনীয় এ নিরাপত্তা ব্যবস্থার ধরন কেমন হবে তার অধিকাংশ নির্ভর করে সে দেশের মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য এবং একাধিক প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতার ওপর।
দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেসব প্রতিষ্ঠানের হাতে ন্যস্ত থাকে এদের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী হিসেবে সাধারণভাবে অভিহিত করা হয়। কোনো নির্দিষ্ট দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাই সে দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রথাগতভাবে এই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে পুলিশ বাহিনী। এ বাহিনীর সামগ্রিক সফলতা বা ব্যর্থতা তাই কোনো দেশের মানবিক উন্নয়নেরও নির্ধারক। বাংলাদেশও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়।
সাম্প্রতিক বছরগুলোয় পুলিশ বাহিনী এবং অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা জনমনে ব্যাপক উদ্বিগ্নতার জন্ম দিয়েছে। ক্রমাগত গুম, হত্যা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় তাদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ রীতিমতো শিউরে ওঠার মতো। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পুলিশ সংস্কারের জন্য ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে ‘পুলিশ সংস্কার কমিশন’ নামে একটি কমিশন গঠন করে এবং ৯০ দিনের মধ্যে একটি প্রতিবেদন প্রধান উপদেষ্টা বরাবর প্রেরণ করার নির্দেশ দেয়।
কমিশনে সাবেক ও বর্তমান আমলা, পুলিশ কর্মকর্তা, আইন বিষয়ক অধ্যাপক, মানবাধিকার কর্মী এবং শিক্ষার্থী প্রতিনিধি রাখা হয়। এ কমিশন ৩১ অক্টোবর ২০২৪ ‘কেমন পুলিশ চাই’ শীর্ষক একটি প্রশ্নমালা অনলাইনে প্রচার করে এবং ১৫ নভেম্বরের মধ্যে মতামত প্রদানের অনুরোধ করে। এতে ২৪,৪৪২ জন উত্তরদাতা তাদের মতামত প্রদান করে। এছাড়া কমিশন বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ এবং অ্যাকাডেমিক ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকেও মতামত গ্রহণ করে। সব তথ্য, উপাত্ত ও পরামর্শ যাচাই করা শেষে ইতিমধ্যে কমিশন তাদের প্রতিবেদন জমা দেয়।
কমিশনের প্রতিবেদনে পুলিশ বাহিনীর সংস্কারে বেশকিছু কার্যকরী পদক্ষেপের কথা বলা হয়। এতে ২২টি আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাতে প্রয়োজনীয় সংশোধন বা পরিবর্তনের ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করার পাশাপাশি অবৈধ জনসমাবেশ ভঙ্গ করার জন্য ৫ ধাপে বলপ্রয়োগের রীতি, রিমান্ডে স্বচ্ছ কাঁচের ঘেরাটোপ দেওয়া জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষ, অভিযান পরিচালনার সময় জিপিএস ট্র্যাকিং সিস্টেম ও শরীরে সংযুক্ত ক্যামেরা ব্যবহার করা, রাতে গৃহ তল্লাশি করার ক্ষেত্রে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অথবা কোনো গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা, নিরপেক্ষ পুলিশ কমিশন গঠন, ফৌজদারি মামলা তদন্তে বিশেষায়িত দল গঠন করা, থানা বা উপজেলা ভিত্তিক ওভারসাইট কমিটি গঠন করা, অনুমোদিত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর মেনে চলা, বিভাগীয় শহরগুলোয় করোনার (Coroner) নিয়োগ দেওয়া, ফরেনসিক প্রশিক্ষণ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা, ডিএনএ ল্যাব প্রতিষ্ঠা করাসহ অনেক বিষয়ে সুপারিশ করা হয়।
যদিও পুলিশ সংস্কার কমিশন, পুলিশ বাহিনীর আধুনিকীকরণে বেশকিছু চমৎকার পরামর্শ দিয়েছে, তারপরেও বিভিন্ন দেশের পুলিশের ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করে সম্ভাব্য আরও কিছু সংস্কার পুলিশ বাহিনীকে আরও আধুনিক এবং গতিশীল করতে পারে। এ প্রেক্ষিতে কয়েকটি দেশের অভিজ্ঞতা নিয়ে নিবন্ধের পরবর্তী অংশে আলোচনা করার চেষ্টা করছি।
এশিয়া মহাদেশে সফল পুলিশের জন্য বিখ্যাত একটি দেশ হলো জাপান। সে দেশের জাতীয় পর্যায় ও প্রিফেকচার (Prefecture) (বাংলাদেশের জেলার সাথে তুলনা করা যায়) পর্যায়ে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে স্থায়ী পাবলিক সেফটি কমিশন আছে যেগুলো সেখানকার পুলিশ ওভারসাইট বডি হিসেবে কাজ করে। এর ফলে পুলিশের ওপর স্থানীয় জনগণের যৌক্তিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়।
তাছাড়া জাপানের পুলিশের ক্ষেত্রে প্রতিটি থানার অধীনে শহর এবং গ্রামাঞ্চলে যথাক্রমে ‘কোবান (Koban)’ এবং ‘চুজাইশো (Chuzaisho)’ নামক পুলিশ বক্স থাকে। এসব স্থানে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসাররা তাদের নির্দিষ্ট এলাকায় জনগণের সাথে সুসম্পর্ক রাখেন এবং সেখানে নিয়মিত টহল দেন। তারা নিজস্ব এখতিয়ারভুক্ত এলাকার জনগণের মধ্যে বিভিন্ন দ্বন্দ্বের নিরসন এবং হারানো সম্পদ পুনরুদ্ধারের মতো কাজ করার মাধ্যমে জনগণের বিশ্বস্ততা অর্জন করে থাকেন।
সম্প্রতি জাপানের এসব পুলিশ বক্সে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পুলিশ বক্স কাউন্সিলর হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার একটি প্রক্রিয়া চালু হয়েছে যার মাধ্যমে অভিজ্ঞ কর্মকর্তারা তাদের অভিজ্ঞতা প্রয়োগের মাধ্যমে পুলিশিংকে আরও জনবান্ধব করার চেষ্টা করেন। বাংলাদেশের পুলিশও তাদের অবসরপ্রাপ্ত কিছু কর্মকর্তাদের জনগণের বিশ্বস্ততা অর্জনের জন্য নিয়োগ দিয়ে জাপানের এই উদাহরণ কাজে লাগাতে পারে। পুলিশের নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের বিপরীতে জনহিতৈষী এসব কর্মকাণ্ড পুলিশের ওপর জনগণের আস্থা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশের কাছ থেকেও বাংলাদেশ পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিক্ষা নিতে পারে। যেহেতু সেখানে পুলিশ কেন্দ্রীয় কোনো নিয়ন্ত্রণ সংস্থার মাধ্যমে সেই অর্থে নিয়ন্ত্রিত হয় না, কাজেই তাদের কাজের ক্ষেত্রে তারা পর্যাপ্ত স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। এসব সংস্থায় যারা একান্তই পুলিশি দায়িত্ব পালন করে তারা ছাড়া অন্যান্য দায়িত্ব, যেমন প্রশাসনিক কাজ, উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং প্রযুক্তি সংক্রান্ত কাজগুলোয় বেসামরিক কর্মীদের ব্যবহার করা হয়।
এতে প্রশিক্ষিত পুলিশ সদস্যরা মাঠপর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোয় মনোযোগ দিতে পারে। ফলে পুলিশে কাজ করা সবাইকে অস্ত্রের ট্রেনিংসহ সরাসরি আইন প্রয়োগের মতো জটিল কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। আর জনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে সেই বিষয়ে যারা অভিজ্ঞ তাদের সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। খরচ কমানোর সাথে সাথে দক্ষতার সর্বোচ্চ প্রয়োগ এতে নিশ্চিত হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব।
যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন পর্যায়ে সেবা দেওয়ার জন্য বিশেষ পুলিশ রয়েছে যাদের স্পেশাল ডিসট্রিক্ট পুলিশ বলা হয়। যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় সেবা দেওয়ার জন্য রয়েছে ক্যাম্পাস পুলিশ। এরা নির্দিষ্ট স্থানে কাজ করার জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত। এদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যে পুলিশ রয়েছে সেখানে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় শিক্ষার্থীদেরও কাজ করার সুযোগ রয়েছে। এরা সেই নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে সেবা প্রদান করতে পারে। এতে জনগণ উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি পুলিশের প্রতি তাদের বিশ্বাস বেড়ে যায়।
বাংলাদেশেও একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার চেয়ে বেশি শিক্ষার্থী রয়েছে এমন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় এ ধরনের পুলিশি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা যেতে পারে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশেও জনগণের ওভারসাইট নিশ্চিত করার অনেকগুলো সংস্থা রয়েছে যাদের উদ্যোগে আশির দশকের পর থেকে তাদের পুলিশে গুণগত মান অনেক বেড়েছে। এটিও বাংলাদেশের জন্য অনুকরণীয় হতে পারে।
তাছাড়া স্থানীয় থানাগুলো তাদের নিজস্ব এলাকার সমস্যাগুলো সমাধানের উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন যেটি যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশিং-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। উপরন্তু জেলা, বিভাগীয় এবং জাতীয় পুলিশের মধ্যে সমন্বয় জোরদার করে কর্তৃত্বের কেন্দ্রিকতা কমানো যেতে পারে এবং স্থানীয় পর্যায়ে সমস্যা সমাধানে সৃজনশীল হওয়ার সুযোগ বাড়ানো যেতে পারে।
ইউরোপের প্রতিনিধিত্বকারী দেশ হিসেবে সুইডিশ পুলিশের কাছ থেকেও বাংলাদেশের পুলিশের বেশকিছু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তারা মানবাধিকার রক্ষায় অত্যন্ত সংবেদনশীল। তারা জনসম্পৃক্ততা ও কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থার মাধ্যমে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পুলিশিং করে থাকে। তারা পুলিশের মানবাধিকার রক্ষা, পেশাদারিত্ব বৃদ্ধি, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করা প্রভৃতি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে।
মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোনো ঘটনায় পুলিশের দায়মুক্তির সুযোগ সেখানে নেই। তাদের বেশ কয়েকটি এক্সটারনাল ওভারসাইট বডি রয়েছে যারা পুলিশের কার্যক্রমকে প্রতিনিয়ত মূল্যায়ন করে থাকে। এগুলোর কোনোটা তারা আইন মেনে কাজ করছে কিনা তা দেখে, কোনটা ব্যক্তিগত তথ্য, কীভাবে ব্যবহার করছে সেটি দেখে, কোনটা পুলিশের কর্মক্ষমতা নিরীক্ষা করে, কোনটা ক্ষমতার অপব্যবহার হচ্ছে কিনা দেখে, কোনটা দেখে তাদের কাজের পরিবেশ কেমন সেটি।
ইউরোপের আরেকটি দেশ যুক্তরাজ্যের ইংল্যান্ডে প্রচলিত পুলিশিং থেকেও আমাদের দেশের পুলিশ বেশকিছু বিষয় অনুসরণ করতে পারে। সেখানে পুলিশের অসদাচরণ বিষয়ে তদন্তের মাধ্যমে পুলিশে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে Independent Office for Police Conduct (IOPC) এর মতো স্বাধীন তদারকি সংস্থা রয়েছে। এর মাধ্যমে পুলিশ কর্মকর্তাদের গুরুতর স্খলনের ব্যাপারে জনগণের অভিযোগ আমলে নেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসে পুলিশের প্রতি জনগণের আস্থা বাড়ানোর জন্য জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এই স্বাধীন সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পুলিশের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে এ ধরনের স্বাধীন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।
এখানে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে শুধু ইংল্যান্ডেই নয়, পুরো যুক্তরাজ্যে পুলিশ সাধারণভাবে অস্ত্র বহন না করে অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। বিশেষ প্রয়োজন হলে তারা অস্ত্র বহনে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ব্যবহার করে থাকে। এটি মানবাধিকার রক্ষায় তাদের দায়বদ্ধতার কথা মনে করিয়ে দেয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটি বর্তমান প্রেক্ষাপটে যৌক্তিক মনে না হলেও তাদের স্বয়ংক্রিয় ও মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার থেকে বিরত রাখা উচিত। অস্ত্র বহন আপাতত বন্ধ না করা হলেও অস্ত্রের প্রয়োগ বন্ধ করার ব্যাপারে কঠোর নীতি অবলম্বন এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি।
উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায়, পুলিশি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এ বাহিনীর সদস্যদের দায়বদ্ধ রাখা একটি সাধারণ ও সর্বজনীন ব্যাপার। তাদের হাতে ক্ষমতা থাকে তাদের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করা আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই বেশিরভাগ সভ্য দেশেই পুলিশের ক্ষমতা ও আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থায়ী ওভারসাইট বডি রয়েছে।
বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও একাধিক স্তরে স্থায়ীভাবে এ ব্যবস্থা থাকা জরুরি। পাশাপাশি পুলিশকে মানবাধিকারের ব্যাপারে আরও বেশি সচেতন করতে হবে। প্রয়োজনে বিদেশি বিশেষজ্ঞ দেশে আনার মাধ্যমে আমাদের দেশের পুলিশে গুণগত পরিবর্তনের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে। তবেই পুলিশের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় লাগাম টানা সম্ভব হবে।
পরিশেষে একটি কথা বলতে চাই, পুলিশি কার্যক্রম এমন কোনো ব্যাপার নয় যেটি একান্তই আমাদের নিজস্ব। পৃথিবীর প্রায় সব আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সরকারি ব্যবস্থাপনায় পুলিশ রয়েছে। এদের মধ্যে অনেক দেশই বিভিন্ন সংস্কারের মাধ্যমে পুলিশকে যুগোপযোগী এবং আধুনিক করে গড়ে তুলেছে। তাদের অনেকের অভিজ্ঞতা বর্তমানে বাংলাদেশে পুলিশের যে সংকট চলছে তা নিরসনে পথ দেখাতে পারে।
আমাদের এই নিবন্ধের উদ্দেশ্যও সে ব্যাপারে কিছুটা আলোকপাত করা। যদিও অল্প পরিসরে পুলিশের মতো একটি জটিল সংস্থার ব্যাপারে আলোকপাত করা কঠিন, তবুও এটি আমাদের অভ্যন্তরীণ সংকটকে বৈশ্বিক ব্যবস্থার আলোকে দেখার একটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করবে বলেই মনে করছি।
ড. মো. বশীর উদ্দীন খান ।। সহযোগী অধ্যাপক, ক্রিমিনোলজি অ্যান্ড পুলিশ সায়েন্স, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
সম্পর্কিত বিষয়:



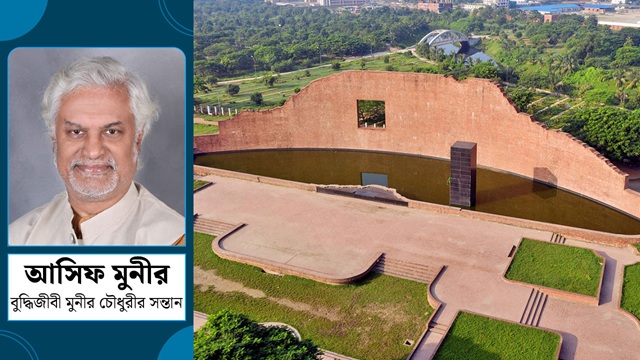

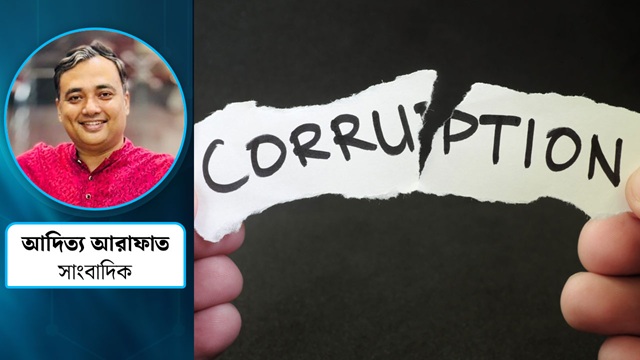



আপনার মূল্যবান মতামত দিন: