হাওর ভরিয়ে হবে বিশ্ববিদ্যালয়, কেন?
প্রকাশিত:
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ১৩:১৭
আপডেট:
২৫ ডিসেম্বর ২০২৫ ১৬:১৭

শিক্ষা মানব জাতির বিকাশ ও পরিপূর্ণতা আনয়নে অন্যতম অনুষঙ্গ। যে জাতি যতবেশি শিক্ষিত সে জাতি তত বেশি উন্নত। মানবিকতার উৎকর্ষতা এবং যোগ্য নাগরিক সৃজনে শিক্ষার বিকল্প নেই। একে আবর্তন করেই সভ্যতা নান্দনিকতা এবং সৌন্দর্যের প্রসার বিস্তৃতি। মানবসমাজ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শিক্ষা নামক প্রপঞ্চের কাছে ঋণী। এ যেন এক অনাবিল অকৃত্রিম পাওয়া যেখানটায় শান্তি স্বকীয়তা গৌরব এবং অস্তিত্বের খোঁজ পাওয়া যায়। শিক্ষার আলোতে অন্ধকার বিদূরিত হয়ে আলোর ঝলকানির দেখা মিলে। সমাজ সংস্কৃতি রাষ্ট্র সংবিধান শিক্ষার মহিমার স্বীকৃতি দিয়েছে। কেননা শিক্ষা মানবের মৌলিক অধিকার ও বটে। সব সরকারই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে নানা পদের সুযোগ-সুবিধা অবকাঠামো সৃষ্টি করে পাহাড়, চা বাগান, হাওর, বাওর, বিলের পাড় সর্বত্র এর প্রসারে কাজ করে যাচ্ছে। এসবে বেসরকারি সংস্থাগুলোর অবদানও চোখে পড়ার মতো। উচ্চশিক্ষা বিস্তারে দেশের নানা অঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা স্থানিক ও সময়ের দাবির প্রতি আগ্রহ ও সমর্থন জানিয়ে মহান সংসদে অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পাস হয়েছে। যৌক্তিকতা এবং প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে সমাজে নানা কথার প্রচলন থাকলেও আজ এসব প্রতিষ্ঠান শিশুকাল পেরিয়ে কৈশোরের দিকে যাত্রা করছে! এত বেশি বিশ্ববিদ্যালয় কি খুব বেশি প্রয়োজন ছিল? প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নির্ধারণে হাওর-বিল-বাওর জলাশয়ের দিকে নজর কেন? এর জন্য কি বিকল্প কোনো স্থান বিবেচনা করা যেত না? জীববৈচিত্রের ঝুঁকি জেনেও কেন এমন কর্মযজ্ঞ? দেশপ্রেম কি শিকেয় উঠলো? ভেবেই বোকা হয়ে যাচ্ছি! এসব কি করে সম্ভব?
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৬ সাল প্রতিষ্ঠিত হয়। যা সিরাজগঞ্জে হওয়ার কথা। যেখানটায় এদেশের সবচেয়ে বড় চলনবিলের আবাস। ছয় জেলার একচল্লিশ উপজেলার একহাজার বর্গ কিলোমিটার জুড়ে এটা বহমান। আর চলনবিলের শেষ মাথায় কি না রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পাস হতে যাচ্ছে! এ কেমন করে সম্ভব? শাহজাদপুর উপজেলার বুরি পোতাজিয়া যেখানটায় অসংখ্য খাল নদসহ অর্ধ শতাধিক নদীর প্রবাহমুখ। ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ১০০ একর ভূমি অধিগ্রহণ করে মাটি ভরাটের কাজ চলছে। চার একর ভূমি ভরাট সম্পন্ন হয়েছে। এ অঞ্চলে বছরে চারমাস পানি থাকে। শুষ্ক মৌসুমে এ অঞ্চল গো-চারণ ভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ২০১৯ সালে এ স্থাপনায় পরিবেশ অধিদপ্তরেরও অনাপত্তি পত্র জুটেছে। এসব কীসের জোর? মাছের আঁধার গোচারণভূমি ধ্বংস করে পরিবেশ ও প্রতিবেশকে কার স্বার্থে ঝুঁকিতে ফেলছি? প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আপাতত প্রশ্ন না করে বিকল্প স্থানে কি ক্যাম্পাসের ঠিকানা করা যেত না? প্রশ্ন থেকেই যায়?
সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ২০২০ সালের ২৬ জুলাইয়ে প্রতিষ্ঠিত। ক্যাম্পাসের স্থান হিসেবে হাওরের কথা বলা আছে। কী হাস্যকর সংযুক্তি? ছাতক দোয়ারাবাজার শান্তিগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা নিয়ে এ জনপদের সবচেয়ে বড় হাওর। যা 'দেখার হাওর' নামেই পরিচিত। এ হাওরের বোরো চাল খ্যাতি দেশজুড়ে। আর এর গর্ভেই কি না সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। মূলত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম ইতিহাসই বেমানান। কৃষি অধ্যুষিত এ জনপদে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হলেই বেশ ভালো হতো এবং প্রকারান্তরে শিল্পাঞ্চল খ্যাত হবিগঞ্জে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ই বেশি মানানসই ছিল। অথচ হয়েছে উল্টো! এখন এসব বলে লাভ নেই। 'দেখার হাওর'-এ মিলিত হয়েছে মহাসিং নদী এবং শাখা প্রশাখা। এখানকার কৃষিজমির পরিমাণ ২৪ হাজার ২১৪ হেক্টর। আর এর কিনারা ঘেঁষেই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ১২৫ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। যার ১২০ একরই বোরো জমি। যেখানে বছরের সাত মাস পানি থাকে এবং শুষ্ক মৌসুমে বোরো আবাদ হয়ে থাকে। দৈব ইশারায় ২০২৩ সালে পরিবেশ অধিদপ্তরের ও অনাপত্তি সনদও পেয়ে গেছে। যদিও ইউজিসির সদস্য প্রফেসর তানজিম উদ্দিন খানের অভিমত হাওর জলাশয় এবং বসতভিটা অধিগ্রহণ করার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নিরোৎসাহিতকরণের বার্তা রয়েছে। তবু্ও থেমে নেই। জুলাই পরবর্তী বাংলায় আশাবাদী ছিলাম এসবের লাগাম টানা হবে! বিপরীতকর্ম দেখে হতাশ! এসব কি দেখার কেউ নেই?
Feasibility study (বাস্তবায়ন যোগ্যতা নিরূপণ) এসব কীভাবে উতরে গেল? ভেবে কুল কিনারা মেলাতে পারি না। অদৃশ্য শক্তির উৎস কোথায়? জলাধার জলজ উদ্ভিদের চারণভূমি দেশীয় মাছের আঁধার ক্ষতিগ্রস্ত করে কীসের উন্নয়ন? ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ সালের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র অনুযায়ী প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ ৫-এ বলা আছে পরিবেশগত স্থায়িত্ব জলবায়ু সহনশীলতা ঝুঁকি ও দুর্যোগ বিশ্লেষণ এবং প্রজ্ঞাপনের ৫.১ এবং ৫.২ ধারায় জলবায়ু পরিবর্তন ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ প্রকল্পের দুর্যোগ সহনশীলতা মূল্যায়ন এসব নির্ধারকের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন সত্ত্বেও কীভাবে ইতিবাচক প্রতিবেদন এসেছে? এসবে কারা জড়িত? খালি চোখে নানা বিপত্তি এবং ঝুঁকি অনুধাবিত হলেও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের চোখে এমনকি রঙিন চশমা ছিল যা প্রকল্পের স্থায়ী ক্যাম্পাসের স্থান নির্বাচনে রসদ জুগিয়েছে? এসবে রাজনৈতিক প্রভাব এবং আধিপত্যই বড় নিয়ামক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিগত সময় প্রভাবশালী মন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপ ছিল। যার কারণে সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জে কলকারখানা মাঝারি ভারি শিল্প প্রতিষ্ঠান না থাকা সত্ত্বেও কারিগরি জনবল তৈরি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির নিমিত্তে বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তার আঞ্চলিক কেন্দ্র এ অঞ্চলে নির্মাণাধীন। বুঝতে কি বাকি আছে কার ইশারায় এসব আয়োজন? গাজীপুর, হবিগঞ্জ এবং ময়মনসিংহের মতো শিল্পপ্রবণ এলাকায়ও এসব নেই কেন?
বাংলাদেশ সরকার পরিবেশ সুরক্ষা এবং জলবায়ুর প্রভাব বিষয়ে বেশ সজাগ। ফলশ্রুতিতে সংবিধানের ১৮(ক) অনুচ্ছেদে জলাভূমি সংরক্ষণ এবং দেখাশোনার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। এসবের ধারাবাহিকতায় জবাবদিহিতা এবং দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার হেতু বাংলাদেশ সরকার ১৯৯২ সালে রামসার কনভেনশনে স্বাক্ষর করে। ১৯৯৫ সালের পরিবেশ সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন এবং এর ১২(৬) ধারায় জলাশয় ভরাটে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়। ২০০০ সালের প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইনে ও পুকুর জলাশয় ভরাটে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। হাওর মাস্টার প্ল্যান এবং জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০০৯ এ টেকসই উন্নয়নের প্রসঙ্গ এসেছে। এতসব যৌক্তিকতা থাকার পরেও কীভাবে এবং কার স্বার্থে হাওর-বাওর ভরাট করে স্থাপনা তৈরির স্বপ্ন? এদের কি ন্যূনতম পরিবেশ ও প্রতিবেশের প্রতি দরদ ও দায়বদ্ধতা নেই?
আমরা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরোধী নই। শিক্ষার প্রসার ও যোগ্য নাগরিক তৈরিতে এর প্রয়োজনীয়তা সর্বজনবিদিত। এসব কার জন্য? সেখানটায় আমাদের পর্যবেক্ষণ। ওয়ান্ডেল বেরি (Wendell Bery)-এর বক্তব্য হলো, পরিবেশ ধ্বংস মানে নিজের সন্তানের ভবিষ্যৎ নষ্ট করা এবং সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানী মার্গারেট মিড (Margaret Mead)-এর আশঙ্কা হলো, পরিবেশ ধ্বংস করলে আমাদের সমাজ থাকবে না। মানুষের প্রয়োজনেই সমাজকে টিকিয়ে রাখতে হবে। এসবে আঞ্চলিকতা ও আমিত্ববোধ পরিহার করা খুব প্রয়োজন। যৌক্তিক পর্যালোচনা এবং বাস্তবায়ন নিরীক্ষার আলোকে প্রয়োজনে বিকল্প স্থানে স্থানান্তরের সিদ্ধান্তের মাঝেই উভয়কুল রক্ষার বন্দোবস্ত হতে পারে। তবেই বাঁচবে মানুষ রক্ষা পাবে জীববৈচিত্র্য এবং সংকটে পড়বে না পরিবেশ ও প্রতিবেশ।
ড. মোহাম্মদ আলী ওয়াক্কাস : অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
সম্পর্কিত বিষয়:




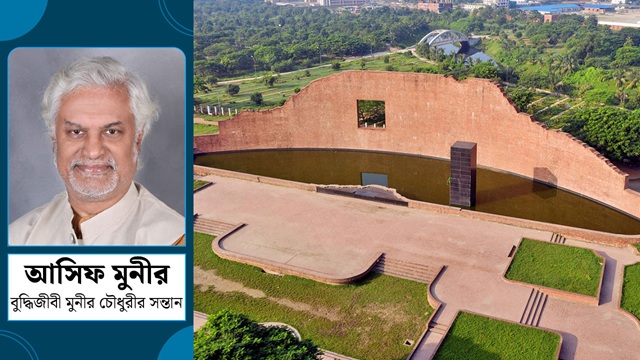

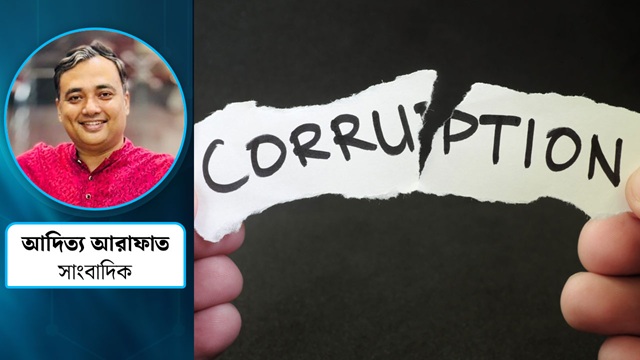




আপনার মূল্যবান মতামত দিন: