ন্যায়বিচার যখন রাষ্ট্রের টিকে থাকার অপরিহার্য শর্ত
প্রকাশিত:
১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ১০:২২
আপডেট:
২৫ ডিসেম্বর ২০২৫ ১৮:২৯

ন্যায়বিচার একটি রাষ্ট্রের প্রাণ, সভ্যতার ভিত্তি এবং জনগণের মৌলিক নিরাপত্তার প্রতীক। ন্যায়বিচার না থাকলে রাষ্ট্র কেবল একটি শক্তিশালী প্রশাসনিক যন্ত্রে পরিণত হয়, যেখানে মানুষের মর্যাদা, অধিকার ও স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে যায়। তাই ইতিহাসের প্রতিটি ধাপে দেখা গেছে যে রাষ্ট্র তখনই টেকসই, সমৃদ্ধ ও উন্নত হয়েছে যখন সেখানে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু ন্যায়বিচার আসলে কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, কেন এর প্রয়োজন, উন্নত রাষ্ট্রে কীভাবে এটি বাস্তবায়িত হয় এবং উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোয় কেন এটি ব্যাহত হয়- এসব প্রশ্নই আমাদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়।
ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মূল শর্ত হলো শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ আইনপ্রণয়ন ও আইন প্রয়োগ ব্যবস্থা। কোনো রাষ্ট্রে সংবিধান ও আইন যদি প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত না করে, তবে সেখানে প্রকৃত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয় না। বিচার বিভাগকে হতে হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ, প্রশাসনকে হতে হবে জবাবদিহিমূলক, আর আইন প্রণয়নকারী ও প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর হতে হবে ন্যায্য, নির্দলীয় ও জনগণের সেবক।
রাজনৈতিক প্রভাব বা অর্থের প্রলোভন যখন আদালত, পুলিশ বা আমলাতন্ত্রে ঢুকে পড়ে, তখন ন্যায়বিচার ভঙ্গুর হয়ে যায়। তবে এসবের পাশাপাশি জনগণের মধ্যেও সচেতনতা ও নৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা জরুরি। কারণ ন্যায়বিচার শুধু আদালতের কাঠগড়ায় নয়, সামাজিক সম্পর্কেও প্রতিফলিত হয়। সমাজে ক্রমাগত বিশৃঙ্খলা কোনোভাবেই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উপযোগী হয় না। এমনকি নিয়োগে যোগ্যতার পরিবর্তে পক্ষপাতিত্ব, ব্যবসায় মুনাফার নামে প্রতারণা, কিংবা লিঙ্গ-বৈষম্যের কারণে নারীর অধিকার খর্ব হওয়া-এসব কিছুই ন্যায়বিচারের পরিপন্থী।
ন্যায়বিচারের প্রয়োজন কেন? এর উত্তর স্পষ্ট। ন্যায়বিচার মানুষের মৌলিক অধিকার ও মর্যাদাকে সুরক্ষা দেয়, দুর্বলকে শক্তির সামনে সমান করে তোলে, শোষিতকে মুক্তি দেয় এবং সমাজে শান্তি ও স্থিতি নিশ্চিত করে। অন্যদিকে ন্যায়বিচারহীন রাষ্ট্রে জন্ম নেয় অবিশ্বাস, হতাশা ও বৈষম্য। তখন মানুষ আইন হাতে তুলে নেয়, সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে, আর অবশেষে রাষ্ট্র অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে।
ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, অন্যায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা কোনো রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্য দীর্ঘদিন টেকেনি। তাই ন্যায়বিচার শুধু একটি নৈতিক আদর্শ নয় বরং রাষ্ট্র টিকে থাকার জন্য অপরিহার্য শর্ত। ইতিহাসবিদরা বলেন, রোমান সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ ছিল শাসকদের অন্যায় শাসন, প্রশাসনে দুর্নীতি এবং নাগরিকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ। ন্যায়বিচারের অভাব মানুষকে রাষ্ট্র থেকে বিমুখ করে তোলে এবং অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও সংঘাতকে উসকে দেয়। ফলে শক্তিশালী সাম্রাজ্য ধ্বসে পড়ে।
ফ্রান্সে দীর্ঘদিন ধরে রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা দরিদ্র জনগণের ওপর নিপীড়ন চালায় এবং ধনীরা আইনের বাইরে থেকে যায়। এই চরম বৈষম্য ও অন্যায়ই জনঅসন্তোষকে বিস্ফোরিত করে ফরাসি বিপ্লব ঘটায়। অর্থাৎ ন্যায়বিচার না থাকলে জনগণ আইন হাতে তুলে নিতে বাধ্য হয়।
বহু বছর ধরে দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগুরু কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠীর ওপর বৈষম্যমূলক আইন চাপিয়ে দেয়। ন্যায়বিচারের এই ঘাটতি দেশটিকে সহিংসতা, আন্তর্জাতিক অবরোধ এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার দিকে ঠেলে দেয়। অবশেষে নেলসন ম্যান্ডেলার নেতৃত্বে বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন সফল হয় এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।
এ পর্যায়ে উন্নত রাষ্ট্রে ন্যায়বিচারের প্রয়োগ নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই। উন্নত রাষ্ট্রগুলোয় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয় বহুমাত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, আইনের শাসন ও শক্তিশালী গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির মাধ্যমে। উদাহরণস্বরূপ, উত্তর ইউরোপের দেশগুলোয় আইনের শাসন শুধু লিখিত আইন নয় বরং সামাজিক বাস্তবতা।
সেখানকার আদালত রাজনৈতিক ক্ষমতার কাছে নত হয় না, সংবাদমাধ্যম স্বাধীনভাবে দুর্নীতি প্রকাশ করতে পারে, প্রশাসন তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে এবং সাধারণ মানুষ আদালতের দ্বারস্থ হতে ভয় পায় না, কারণ বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত, সুলভ ও কার্যকর। এছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা এত শক্তিশালী যে ধনী-গরিবের মধ্যে বৈষম্য কম থাকে, ফলে ন্যায়বিচারের ধারণা বাস্তবে প্রতিফলিত হয়।
যুক্তরাষ্ট্রে ‘চেকস অ্যান্ড ব্যালান্সেস’ নীতির মাধ্যমে নির্বাহী, আইনসভা ও বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য রাখা হয় যাতে কোনো একক প্রতিষ্ঠান সর্বময় ক্ষমতা না পায়। এ ব্যবস্থাই সেখানে ন্যায়বিচার রক্ষায় বড় ভূমিকা রাখে। অন্যদিকে জাপান বা দক্ষিণ কোরিয়ায় ন্যায়বিচার শুধু আদালতে সীমাবদ্ধ নয়; সেখানে শিক্ষা, নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার মাধ্যমে মানুষকে এমনভাবে গড়ে তোলা হয় যে অন্যায় করলে সে সামাজিকভাবে লজ্জিত হয়। অর্থাৎ ন্যায়বিচার শুধু প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে নয়, সামাজিক মানসিকতাতেও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত।
এ প্রসঙ্গে না বললেই নয় যে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোয় ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এত সহজ নয়। এখানে বিচারব্যবস্থা প্রায়শই রাজনৈতিক প্রভাব, দুর্নীতি, মামলা নিষ্পত্তির ধীরগতি, আর্থিক অক্ষমতা ও সামাজিক বৈষম্যের কারণে ব্যাহত হয়। আইনের শাসনকে প্রায়ই ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে।
দুর্বল ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ন্যায়বিচার পেতে বাধার মুখে পড়ে। অনেক সময় মামলার দীর্ঘসূত্রতা ও বিচার ব্যয়ের কারণে মানুষ আদালতের দ্বারস্থ হতেও ভয় পায়। সংবাদমাধ্যম ও নাগরিক সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, ফলে দুর্নীতি ও অনিয়ম প্রকাশ পায় না। এর ফলে ন্যায়বিচারের ধারণা শুধু কাগজে-কলমে থেকে যায়, বাস্তবে মানুষের জীবনে প্রতিফলিত হয় না।
দার্শনিকরা ন্যায়বিচার নিয়ে নানা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্লেটো (Plato) তার The Republic গ্রন্থে বলেছেন, ন্যায়বিচার হলো প্রত্যেকে নিজের কাজ সঠিকভাবে করা এবং অপরের কাজে হস্তক্ষেপ না করা। এরিস্টটল (Aristotle) ন্যায়বিচারকে ভাগ করেছেন বণ্টনমূলক (distributive) ও প্রতিকারমূলক (corrective) দুই ভাগে, যেখানে প্রথমটি সম্পদ ও সুযোগের ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত করে, আর দ্বিতীয়টি অন্যায়ের প্রতিকার করে।
জন রলস (John Rawls) তার আধুনিক তত্ত্বে বলেছেন, ন্যায়বিচার মানে হলো ‘ন্যায্যতা’ (justice as fairness), যেখানে সামাজিক চুক্তির ভিত্তিতে সবাই এমন নিয়ম মেনে চলবে যা দুর্বলদেরও সুরক্ষা দেবে। তার ‘veil of ignorance’ ধারণায় বলা হয়, আমরা যদি না জানতাম সমাজে আমরা ধনী না গরিব, শক্তিশালী না দুর্বল হয়ে জন্ম নেবো, তবে আমরা এমন নিয়ম বানাতাম যা সবার জন্য সমানভাবে ন্যায্য হবে।
অন্যদিকে অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলেছেন, ন্যায়বিচার মানে শুধু প্রতিষ্ঠান নয়, বরং মানুষের স্বাধীনতা ও সামর্থ্যের প্রসার ঘটানো। কারণ ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য হলো মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, কেবল আইনের চোখে সমতা নয়।
ব্রিটিশ রাজনৈতিক দার্শনিক ডাডলি নোলস (Dudley Knowles) তার Political Philosophy বইয়ে উল্লেখ করেন, ন্যায়বিচারকে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব থেকে আলাদা করে দেখা যায় না। রাষ্ট্রের আইন যদি বৈধ ও ন্যায্য হয়, তবে তা মানা নাগরিকের কর্তব্য।
অর্থাৎ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা না হলে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বও প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। তিনি হবস (Hobbes), লক (Locke) ও রুসোর ( Rousseau) সামাজিক চুক্তির ধারণাকে নতুন করে ব্যাখ্যা করেছেন। তার মতে, রাষ্ট্রের বৈধতা নির্ভর করে নাগরিকদের সম্মতি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার ক্ষমতার ওপর। যদি রাষ্ট্র ন্যায়বিচার দিতে ব্যর্থ হয়, তবে সামাজিক চুক্তির ভিত্তি নষ্ট হয়ে যায়।
নোলস জন রলসের Justice as Fairness ধারণার সঙ্গে একমত হলেও আরও জোর দেন সমান সুযোগ ও নাগরিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তার ওপর। তার মতে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা তখনই সম্ভব যখন রাষ্ট্র দুর্বল ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষা করবে এবং কেবল শক্তিশালী গোষ্ঠীর স্বার্থ দেখবে না।
নোলস বলেছেন, ন্যায়বিচার শুধু আইন দিয়ে নির্ধারিত নয়; এটি একটি নৈতিক নীতি। কোনো আইন যদি নৈতিকভাবে অন্যায় হয়, তবে সেটি বৈধ হলেও ন্যায়বিচার হতে পারে না। তার মতে, গণতন্ত্রই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি। কারণ গণতান্ত্রিক সমাজে মানুষ সমানভাবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে, আর জনগণের ইচ্ছার ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন হলে তা অধিকতর ন্যায্য হয়।
এসব বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট হয় যে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মূল শর্ত হলো সমতা, স্বাধীনতা, অংশগ্রহণ ও দায়বদ্ধতা। উন্নত রাষ্ট্রগুলোয় এ নীতিগুলো বাস্তবে প্রতিফলিত হলেও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোয় তা প্রায়শই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই আমাদের মতো রাষ্ট্র যদি শুধু আইন রক্ষায় ব্যবহৃত হয় আর দুর্বলরা উপেক্ষিত হয়, তবে সেটি প্রকৃত ন্যায়বিচার নয়।
ন্যায়বিচারের জন্য দরকার স্বাধীন বিচারব্যবস্থা, স্বচ্ছ প্রশাসন, জবাবদিহিমূলক রাজনীতি এবং নাগরিকদের নৈতিক চেতনা। উন্নত রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের উচিত ন্যায়বিচারের ধারণাকে আদালতের কক্ষ বা আইন বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ না রেখে তা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিষ্ঠা করা, যাতে কর্মসংস্থানে হয় যোগ্যতার মূল্যায়ন, ব্যবসায় হয় সততা, রাজনীতিতে হয় নৈতিকতা আর সমাজে হয় সমতা।
তবেই আমরা এমন একটি রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারব যেখানে ন্যায়বিচার কেবল স্লোগান নয়, বরং প্রতিটি নাগরিকের বাস্তব অভিজ্ঞতা। কারণ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রেই কেবল শান্তি, স্থিতিশীলতা ও টেকসই উন্নয়ন সম্ভব, অন্যথায় অন্যায়ের আগুন একদিন রাষ্ট্রকেই গ্রাস করবে।
ড. সুলতান মাহমুদ রানা : অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
[email protected]
সম্পর্কিত বিষয়:




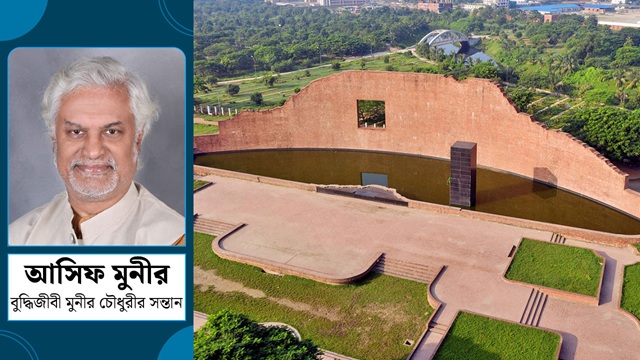

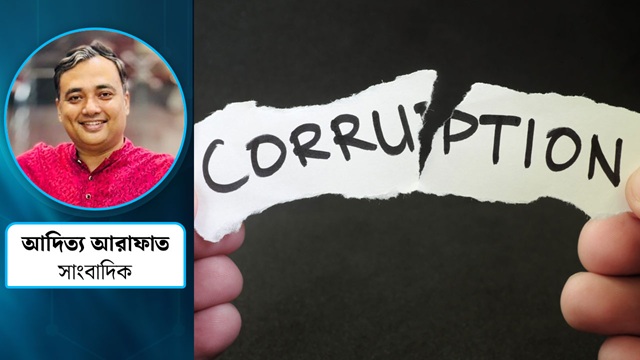




আপনার মূল্যবান মতামত দিন: